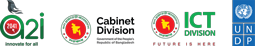চূড়ান্ত সংস্করণ
সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল
(National Integrity Strategy of Bangladesh)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর
জানুয়ারি ২০১৮
|
|
প্রধানমন্ত্রীর বাণী
জাতীয় মুক্তির ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এই দীর্ঘ সংগ্রামের চালিকাশক্তি ছিল একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজের স্বপ্ন। কিন্তু রাষ্ট্রের একচল্লিশ বছরের ইতিহাসে সেই স্বপ্ন বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে, পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং মুখ থুবড়ে পড়েছে। জাতির পিতার শাহাদাত, সামরিক শাসন এবং স্বৈরাচারী, গণবিরোধী ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির ক্ষমতা দখল জনগণের সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নকে বারবার দূরে সরিয়ে দিয়েছে। জনগণের জীবনে এ ধরনের শাসনের কুফল প্রতিফলিত হয়েছিল অনুন্নয়নে, বৃহৎ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অবদমনে, রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনায়, দুর্নীতিতে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শুদ্ধাচারের অভাবে। জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পর আমাদেরকে এই দুঃশাসনের বিরুদ্ধে, অব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং রাষ্ট্রীয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়।
এই যুদ্ধকে আমরা চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করেছি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও তাঁর শাসনামলে একই ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালের ২৫ ডিসেম্বরে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ‘‘... সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না – চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এই অভাগা দেশের ভাগ্য ফেরানো যাবে কি না সন্দেহ। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার ঊর্ধ্বে থেকে আমাদের সকলকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি করতে হবে।’’ আমরাও আমাদের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সকল কাজে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্রনিষ্ঠার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছি।
সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সে আলোকে আইনকানুন, নিয়মনীতি, পরিকল্পনা ও বিভিন্ন কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তাদের বাস্তবায়ন অব্যাহত আছে; দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কেবল রাষ্ট্রীয় নিয়মনীতি, আইনকানুন প্রণয়ন ও প্রয়োগই যথেষ্ট নয়; তার জন্য সামগ্রিক এবং নিরবচ্ছিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সামগ্রিক উদ্যোগের সহায়ক কৌশল হিসাবে ‘সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ প্রণয়ন করা হয়েছে।
এই কৌশলটি বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ এবং বেসরকারি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। চরিত্রনিষ্ঠা আনয়নের জন্য মানুষের জীবনের একেবারে গোড়া থেকে, পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। রাজনীতিতেও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১১-২০১৫) আমরা সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি দমনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছি। ‘রূপকল্প ২০২১’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত ‘বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১’ শীর্ষক দলিলে দুর্নীতি দমনকে একটি আন্দোলন হিসাবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। এই আন্দোলনে সবাইকে অংশীদার হতে হবে।
আমরা সবাইকে এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানাই।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
শেখ হাসিনা
মুখবন্ধ
রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য ও দায়িত্ব হল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, সমতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নেই রাষ্ট্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য কৌশল হল সমাজ ও রাষ্ট্রকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা এবং দেশে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা।
দীর্ঘ স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশ উল্লিখিত মহান আদর্শকে রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে স্থির করেছিল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ‘মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ’ রাষ্ট্র-পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে এবং ‘অনুপার্জিত আয়’কে সর্বতোভাবে বারিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। এই নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সরকার অব্যাহতভাবে দুর্নীতি দমনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং এরই সুসমন্বিত উদ্যোগ হিসাবে ‘সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ শিরোনামে এই জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলটি প্রণয়ন করা হয়েছে।
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, “নেশন মাস্ট বি ইউনাইটেড অ্যাগেইনস্ট করাপশন। পাবলিক ওপিনিয়ন মবিলাইজ না করলে শুধু আইন দিয়ে করাপশন বন্ধ করা যাবে না।” দুর্নীতি দমন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় বহুবিধ আইন, বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর আরও কিছু নতুন আইন প্রণয়ন করেছে, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উন্নয়নে বেশ কিছু নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে এবং এগুলির ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করেছে। কিন্তু দুর্নীতিকে কেবল আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে দমন করা সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। এই কৌশলপত্রটিতে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পদ্ধতিগত সংস্কার, তাদের কৃত্য, কৃতি এবং দক্ষতার উন্নয়ন এবং সর্বোপরি একটি সমন্বিত ও সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে শুদ্ধাচারকে একটি আন্দোলন হিসাবে গড়ে তোলার রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে।
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান দলিলপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে; সরকারি কর্মকর্তা, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন, সুশীল সমাজ ও নাগরিকগোষ্ঠীর সঙ্গে পরামর্শসভা আয়োজনের মাধ্যমে তাদের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে; মাননীয় সংসদ সদস্য ও অন্যান্য অংশীজনের অভিমত গ্রহণ করা হয়েছে। জনমত যাচাইয়ের জন্য খসড়া কৌশলপত্রটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করা হয়েছিল। কৌশলপত্রটি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের লিখিত মতামতও গ্রহণ করা হয়েছে। খসড়াটি পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রিসভা কর্তৃক মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কয়েকটি সভায় মিলিত হয়ে দলিলটির কাঠামো ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে যেসব মতামত ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন সেগুলির আলোক সার্বিকভাবে এই দলিলটি বিন্যস্ত করা হয়েছে। গত ১৮ অক্টোবর ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে কৌশলপত্রটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়।
এই দলিলটি প্রণয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে এবং এর খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিসভা কর্তৃক গঠিত কমিটির সকল সম্মানিত সদস্যকে তাঁদের উপদেশ ও নির্দেশনার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এ বিষয়ে মূল্যবান দিক্-নির্দেশনা প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। দলিলটি পর্যালোচনান্তে অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সংশ্লিষ্ট সকল রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং এদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ এই দলিলে বিধৃত কার্যাবলিতে যুক্ত হয়ে শুদ্ধাচারকে একটি আন্দোলন হিসাবে গড়ে তুলবেন এবং তাতে উৎকর্ষ আনয়ন করবেন।
মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
সূচিপত্র
পৃষ্ঠা
নির্বাহী সারসংক্ষেপ ঘ-ঙ
অধ্যায় ১: পটভূমি ১
- ভূমিকা ১
- শুদ্ধাচারের ধারণা ১
- শুদ্ধাচারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আইনকানুন ও নিয়মনীতি এবং গৃহীত পদক্ষেপ ১
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের যৌক্তিক ভিত্তি ২
১.৫ জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থা ৩
১.৬ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য ৪
অধ্যায় ২: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল – রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ৫
২.১ নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন ৫
২.২ জাতীয় সংসদ ৭
২.৩ বিচার বিভাগ ৯
২.৪ নির্বাচন কমিশন ১১
২.৫ অ্যাটর্নি জেনারেল ১২
২.৬ সরকারি কর্ম কমিশন ১৩
২.৭ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ১৪
২.৮ ন্যায়পাল ১৬
২.৯ দুর্নীতি দমন কমিশন ১৬
২.১০ স্থানীয় সরকার ১৮
অধ্যায় ৩: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল – অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ২০
৩.১ রাজনৈতিক দল ২০
৩.২ বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ২১
৩.৩ এনজিও ও সুশীল সমাজ ২২
৩.৪ পরিবার ২৪
৩.৫ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ২৪
৩.৬ গণমাধ্যম ২৫
অধ্যায় ৪: বাস্তবায়ন ও উপসংহার ২৭
৪.১ বাস্তবায়ন ব্যবস্থা ২৭
৪.২ পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা ২৭
৪.৩ উপসংহার ২৮
নির্বাহী সারসংক্ষেপ
১. বাংলাদেশ একটি উদীয়মান, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, স্বল্পোন্নত রাষ্ট্র। এই জাতির লক্ষ্য ‘রূপকল্প ২০২১’-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, আগামী এক দশকে দেশটিতে ক্ষুধা, বেকারত্ব, অশিক্ষা, বঞ্চনা ও দারিদ্র্য থাকবে না। দেশে বিরাজ করবে সুখ, শান্তি, সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধি। সংবিধানের প্রস্তাবনা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ‘এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা’ হবে, ‘যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত’ হবে। সরকার বিশ্বাস করে যে, এই লক্ষ্য পূরণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রের অবশ্য-কর্তব্য, এবং সেই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিপালন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য পরাকৌশল। ঐতিহ্যগতভাবে লব্ধ এবং বর্তমান সরকারের আমলে গঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং প্রণীত আইনকানুন, বিধিবিধান ও পদ্ধতি সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। কিন্তু কেবল আইন প্রয়োগ ও শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে একটি আন্দোলন গড়ে তোলা, যাতে নাগরিকগণ চরিত্রনিষ্ঠ হয়, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ও সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা পায়। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই একটি কৌশল-দলিল হিসাবে ‘সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ প্রণয়ন করা হয়েছে।
২. ২০০৮ সালের নির্বাচনে ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দলের নির্বাচনী ইশতেহারেও ‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণের’ প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত হয়েছিল। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে সরকার সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত তিন বছর নয় মাসে সরকার ১৮০ টি আইন ও ৩৩টি কর্মকৌশল ও নীতি প্রণয়ন করেছে। দুর্নীতি দমনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম যেসব আইন প্রণীত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: ‘সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯’, ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’, ‘ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯’, ‘সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯’, ‘জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯’, ‘চার্টার্ড সেক্রেটারিজ আইন, ২০১০’, ‘জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১’, ‘মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২’, ‘মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২’, ‘প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২’, ইত্যাদি। এক্ষণে সুশাসন প্রতিষ্ঠায়, এবং আরও সুনির্দিষ্টভাবে দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় এসব আইনের প্রয়োগ ও কার্যকারিতার মূল্যায়ন প্রয়োজন, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সংযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। সেইসঙ্গে এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কর্মধারা নির্ধারণও জরুরি হয়ে পড়েছে। এই শুদ্ধাচার কৌশলটি সে লক্ষ্যেই গৃহীত একটি উদ্যোগ । দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা এবং তাদের ভবিষ্যৎ-কৌশল চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়নে এই কৌশল-দলিলটি সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
৩. বাংলাদেশ জাতিসংঘের United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)-এর অনুসমর্থনকারী দেশ। দুর্নীতি নির্মূলের জন্য ‘ফৌজদারী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে দুর্নীতির প্রতিকার ছাড়াও দুর্নীতির ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণকে’ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই কনভেনশনে। বাংলাদেশের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৬) এবং ‘রূপকল্প ২০২১’ এবং ‘পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১’-এও সমধর্মী কর্মসূচি চিহ্নিত করা হয়েছে। এই দলিলে বিধৃত কর্ম-পরিকল্পনাসমূহ উল্লিখিত কনভেনশন ও পরিকল্পনাসমূহের লক্ষ্য অর্জনে প্রণীত একটি সমন্বিত কৌশল।
৪. শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তি-পর্যায়ে এর অর্থ হল কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা, তথা চরিত্রনিষ্ঠা। এই দলিলটিতে শুদ্ধাচারের এই অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে।
৫. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনই পরিবার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ ও এনজিও এবং শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সাকুল্যে অরাষ্ট্রীয় হিসাবে চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকাও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ তিনটি অঙ্গে বিভক্ত – বিচার বিভাগ. আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগ। তারা স্বাধীন সত্তায় তাদের নিজস্ব কর্মবৃত্তে যথাক্রমে বিচারকার্য, রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ও নির্বাহীকার্য পরিচালনা করে। সংবিধান অনুযায়ী গঠিত আরও কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন, নির্বাচন কমিশন, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি কর্ম কমিশন, ন্যায়পাল, যারা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠিত এবং যারা বাজেট ও আর্থিক নিয়মাবলি অনুসরণ সাপেক্ষে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে তাদের কর্মসম্পাদন করে। অন্য আরও কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা আলাদা আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট, এবং ‘সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ’ হিসাবে অভিহিত; যেমন, দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, ইত্যাদি। সংবিধানে স্থানীয় শাসনের যে-ব্যবস্থা নির্দেশ করা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম ও শহরের স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান যেমন, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন গঠন করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানের সকলের ভূমিকাকেই গুরুত্ব প্রদান জরুরি।
৬. এই দলিলটিতে রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আইনকানুন ও বিধিবিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ, তাদের পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের চরিত্রনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীতব্য কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হয়েছে তারা হল: রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১. নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন, ২. জাতীয় সংসদ, ৩. বিচার বিভাগ, ৪. নির্বাচন কমিশন, ৫. অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, ৬. সরকারি কর্ম কমিশন, ৭. মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ৮. ন্যায়পাল, ৯. দুর্নীতি দমন কমিশন, ১০. স্থানীয় সরকার এবং অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১. রাজনৈতিক দল, ২. বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ৩. এনজিও ও সুশীল সমাজ, ৪. পরিবার, ৫. শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও ৬. গণমাধ্যম। এই কৌশলটির রূপকল্প হল ‘সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা’ – রাষ্ট্র এবং সমাজ হিসাবে এটিই বাংলাদেশের গন্তব্য; আর সেই গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য রাষ্ট্রে ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সবচেয়ে জরুরি কাজ। ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কৌশল হিসাবে বিবেচিত এবং সরকার গুরুত্বপূর্ণ একটি অবলম্বন হিসাবে এটি প্রণয়ন করছে।
৭. উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অব্যাহতভাবে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে চলেছে। এগুলিতে পদ্ধতিগত সংস্কারও সাধন করা হচ্ছে। তবে বর্তমানে এসব কার্যক্রম ও সংস্কার-উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও এগুলির একটি সম্মিলিত রূপ প্রদানের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে – এই কৌশলটিতে সে উদ্যোগই নেওয়া হয়েছে। চিহ্নিত সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তাদের কৃত্য, কৃতি, বিবর্তন, বর্তমান অবস্থা ও তাদের চ্যালেঞ্জ তুলে ধরা হয়েছে এবং প্রত্যেকের জন্য আলাদা কর্মপরিকল্পনা বিধৃত করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনায় বাস্তবায়নকাল হিসাবে স্বল্পমেয়াদ (এক বছরের মধ্যে), মধ্যমেয়াদ (তিন বছরের মধ্যে) এবং দীর্ঘমেয়াদ (পাঁচ বছরের মধ্যে) চিহ্নিত করা করা হয়েছে। এই দলিলটিকে নীতিগতভাবে একটি বিকাশমান দলিল হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে এবং এতে সময়ের বিবর্তনে এবং প্রয়োজনের নিরিখে নতুন সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সুযোগ রাখা হয়েছে । প্রতিটি প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানগুচ্ছের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ছকে কার্যক্রম (intervention) চিহ্নিত করা হয়েছেঃ
|
ক্রমিক |
কার্যক্রম |
কর্মসম্পাদন সূচক |
সময় |
দায়িত্ব |
সহায়তাকারী |
৮. মূলত জনপ্রশাসনের মাধ্যমেই সরকার এই কৌশলটি বাস্তবায়ন করবে। কৌশলটিতে রাষ্ট্রের অন্য দুটি অঙ্গ – বিচার বিভাগ ও আইনসভা, এবং সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের জন্যও কর্মসূচি প্রস্তাব করা হয়েছে। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার উচ্চ গুরুত্ব বিবেচনা করে এসব প্রতিষ্ঠান স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে চিহ্নিত পথরেখা অনুসরণে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন এসব প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি সহায়তা ও সম্পদ সরবরাহ করবে। সুশীল সমাজ ও শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও জনপ্রশাসন সহযোগিতা প্রদান করবে এবং কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবে। ‘শুদ্ধাচার কৌশল’টি বাস্তবায়নের জন্য একটি ‘জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ’ গঠন করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদের কয়েকজন সদস্য, কয়েকজন আইনপ্রণেতা, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সচিব, এনজিও ও সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম এবং ব্যক্তিখাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক-প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে এই উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হবে। সুশীল সমাজ, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমের সদস্যগণ পরিষদে সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। এই উপদেষ্টা পরিষদ বছরে অন্ততপক্ষে দু’বার সভায় মিলিত হবে এবং শুদ্ধাচার অনুশীলন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ করবে এবং এ সম্পর্কিত দিক্-নির্দেশনা প্রদান করবে। এই কৌশল-দলিলটির আওতায় চিহ্নিত কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকৃতভাবে বাস্তবায়িত হবে। এতে চিহ্নিত দায়িত্বপালনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে এবং সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাতে সহায়তা প্রদান করবে। প্রতি মন্ত্রণালয়ে ‘নৈতিকতা কমিটি’ ও ‘শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট’ প্রতিষ্ঠা করা হবে। তারা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধাচার ও দুর্নীতি দমন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে এবং পরিবীক্ষণ করবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সচিবালয় হিসাবে কাজ করবে এবং সার্বিকভাবে সকল কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করবে। দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচারকে স্বীকৃতি প্রদান ও উৎসাহিতকরণের জন্য ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার’ প্রবর্তন করা হবে। সেই লক্ষ্যে নির্বাহী বিভাগ, ব্যবসায় খাত ও সুশীল সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে যারা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবেন, তাদের জন্য সরকার বার্ষিক পুরস্কার প্রবর্তন করবে।
৯. এই কৌশলটির রূপকল্প (vision) হচ্ছে সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা। বাংলাদেশ ও তার সংগ্রামী মানুষের এটিই হল কাঙ্খিত গন্তব্য। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য রাষ্ট্র, তার প্রতিষ্ঠানসমূহে ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করবে তা-ই প্রত্যাশিত। শুদ্ধাচার কৌশলকে এ প্রত্যাশা পূরণের একটি অবলম্বন হিসাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, এই কৌশলটির অনুসরণ ও বাস্তবায়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে জনগণ ও জাতির পিতার স্বপ্ন ‘সোনার বাংলা’ প্রতিষ্ঠায় কার্যকর অবদান রাখবে।
অধ্যায় ১
পটভূমি
১.১ ভূমিকা
(ক) বাংলাদেশ একটি উদীয়মান, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, স্বল্পোন্নত রাষ্ট্র। এই জাতির লক্ষ্য ‘রূপকল্প ২০২১’-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, আগামী এক দশকে দেশটিতে ক্ষুধা, বেকারত্ব, অশিক্ষা, বঞ্চনা ও দারিদ্র্য থাকবে না; দেশে বিরাজ করবে শান্তি, সুখ, সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি। সংবিধানের প্রস্তাবনা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ‘এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা’ হবে ‘যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত’ হবে।
(খ) রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ জনগণের মঙ্গল এবং জাতীয় জীবনের সর্বত্র উচ্চাদর্শ প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে ‘জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিতকরণ’ এবং ‘জাতিসংঘের সনদ মেনে চলার’ প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে। ন্যায়ভিত্তিক, দুর্নীতিমুক্ত ও শুদ্ধাচারী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল মানবসত্তার সেই মর্যাদা এবং মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করা সম্ভব। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই সর্বজনীন এসব আদর্শের বাস্তবায়ন এবং সেইসঙ্গে সাংবিধানিক মৌলনীতি পালনে ন্যায়পরায়ণ, দুর্নীতিমুক্ত ও শুদ্ধাচারী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট আছে। নির্বাচনে ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়েছে, ‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ক্ষমতাবান লোকদের বছরওয়ারী সম্পদের বিবরণী দাখিল করতে হবে। ঘুষ, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অর্থ আদায়, চাঁদাবাজি এবং দুর্নীতি দূর করার জন্য কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যারা অনুপার্জিত ও কালো টাকার মালিক, যারা ব্যাংকের ঋণখেলাপি, টেন্ডারবাজ এবং রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে পেশিশক্তি ব্যবহার করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের একাধিপত্য ভেঙ্গে দেওয়া হবে।’ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দলের নির্বাচনী ইশতেহারেও অনুরূপ প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত হয়েছে।
১.২ শুদ্ধাচারের ধারণা
শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তিপর্যায়ে এর অর্থ হল কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা, তথা চরিত্রনিষ্ঠা। এই দলিলটিতেও শুদ্ধাচারের এই অর্থকেই গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যক্তির সমষ্টিতেই প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয় এবং তাদের সম্মিলিত লক্ষ্যই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; সমন্বিত রূপ হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার অনুশীলনও জরুরি। রাষ্ট্রীয় আইনকানুন ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি ও দর্শন এমনভাবে প্রণীত ও অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন যাতে এগুলি শুদ্ধাচারী জীবন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়। বাংলাদেশের সমাজ বিভিন্ন খাত, যথা রাষ্ট্র, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজে বিভিন্ন আইনকানুন, নিয়মনীতি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পালন ও লালন করে শুদ্ধাচার অনুশীলন করে চলেছে এবং সময়ের চাহিদা অনুযায়ী তাতে সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন করছে।
১.৩ শুদ্ধাচারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আইনকানুন ও নিয়মনীতি এবং গৃহীত পদক্ষেপ
(ক) বাংলাদেশের সংবিধানের চেতনা নির্দেশ করে যে, বাংলাদেশ হবে একটি ন্যায়ভিত্তিক, শুদ্ধাচারী সমাজ; এর নাগরিকবৃন্দ, পরিবার, রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজও হবে দুর্নীতিমুক্ত ও শুদ্ধাচারী। ব্যক্তিমানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা ও অধিকার সংরক্ষণ এবং সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রের আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রণীত হয়েছে এবং অনুসৃত হচ্ছে। ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে গৃহীত আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনায় কতিপয় মূলনীতি নির্ধারিত হয়। সেই অনুযায়ী আমাদের প্রত্যয় হল:
১. মানুষের উপর মানুষের শোষণ থেকে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিতকরণ (১০ অনুচ্ছেদ);
২. মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ (১১ অনুচ্ছেদ);
৩. মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিতকরণ (১১ অনুচ্ছেদ);
৪. সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ (১৯ অনুচ্ছেদ);
৫. নাগরিকের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন ও সুষম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ (১৯ অনুচ্ছেদ);
৬. জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ (১৯ অনুচ্ছেদ);
৭. প্রত্যেকের যোগ্যতা বিবেচনা করে কর্মানুযায়ী পারিশ্রমিক নিশ্চিতকরণ (২০ অনুচ্ছেদ);
৮. কোন ব্যক্তিকে অনুপার্জিত আয় ভোগ থেকে অসমর্থকরণ (২০ অনুচ্ছেদ)।
এই সূত্রে রাষ্ট্র ও সমাজে কার্যকরভাবে ন্যায় ও সততা প্রতিষ্ঠা এবং সফলতার সঙ্গে দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা সরকারের একটি মূল নীতি।
(খ) যে কোনও ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ কিংবা সুযোগ ব্যবহারের উদ্যোগে দুর্নীতি সংঘটিত হতে পারে। সেজন্য দুর্নীতি প্রতিরোধের বিধান সুদূর অতীত থেকেই চালু রয়েছে। ১৮৬০ সালের Penal Code-এ দুর্নীতি প্রতিরোধের বিধান রয়েছে। ১৯৪৭ সালে দুর্নীতি দমন আইন পাশ হয়। ২০০৪ সালের ৫ নম্বর আইনে ‘দেশে দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কার্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি ও অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার জন্য একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান’ প্রণীত হয়। এই আইনের আওতায় যেসব কার্য অপরাধ বলে বিবেচিত হয় তা হল: ‘(খ) The Prevention of Corruption Act, 1947 (Act 11 of 1947)-এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ; (গ) The Penal Code 1860 (Act XLV of 1860)-এর sections 161-169, 217, 218, 408, 409 and 477A-এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধসমূহ;’ এবং এসব অপরাধের সঙ্গে সংযুক্ত সহায়তাকারী ও ষড়যন্ত্রমূলক ও প্রচেষ্টামূলক অপরাধকার্য। সম্প্রতি প্রণীত ‘মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২’-এর আওতাধীন অপরাধও দুর্নীতি হিসাবে বিবেচিত। সহজ বর্ণনায় এসব অপরাধ হল সরকারি কর্মচারীদের বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত অন্যবিধ বকশিশ গ্রহণ; সরকারি কর্মচারীদের অসাধু উপায়ে প্রভাবিত করার জন্য বকশিশ গ্রহণ; সরকারি কর্মচারী কর্তৃক বিনামূল্যে মূল্যবান বস্তু গ্রহণ; কোনও মানুষের ক্ষতি সাধনার্থে সরকারি কর্মচারীদের আইন অমান্যকরণ; সরকারি কর্মচারীর বেআইনি ব্যবসা পরিচালনা; কাউকে সুবিধা প্রদানের জন্য সরকারি কর্মচারী কর্তৃক আইনের নির্দেশ অমান্যকরণ, ভুল রেকর্ড ও লিপি প্রস্ত্ততকরণ; অসাধু উপায়ে সম্পত্তি আত্মসাৎকরণ; অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ; প্রতারণা; জালিয়াতি; সরকারি নথিপত্র ও রেজিষ্টার, জামানত, উইল ইত্যাদি জালকরণ; হিসাবপত্র বিকৃতকরণ, অর্থ পাচার, ইত্যাদি। অন্যবিধ আর্থিক দুর্নীতি, অনুপার্জিত সম্পত্তিলাভ ও ভোগ, অর্থসম্পত্তি পাচারের দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য আয়কর আইনে কৃত অপরাধকেও দুর্নীতিমূলক অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। কেবল জনপ্রশাসনেই নয়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজ ও এনজিও-র দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে দুর্নীতি দমন আইন কার্যকর আছে। সরকার কর্তৃক অনুসৃত ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়ন ও দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬’ ও ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮’ অনুসৃত হয়। এনজিওদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের জন্য সরকার প্রণীত আইনি ও নিয়ন্ত্রণমূলক নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয়। শিল্প, ব্যবসা-বণিজ্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক আইনসমূহ প্রযোজ্য হয়। সামগ্রিকভাবে এই সকল আইনকানুন ও নিয়মনীতি শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপালনে অবদান রাখে।
(গ) প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধন, নতুন নিয়মনীতি প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে নিরন্তর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সরকার রাষ্ট্রে ও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সরকার দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করেছে। ‘মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২’-এর সুষ্ঠু প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ‘জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন, ২০১১’ প্রণয়ন করে দুর্নীতি সংঘটন সম্পর্কিত ঘটনার সংবাদদাতাদের সুরক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করে দুর্নীতি প্রতিরোধকে জোরদার করা হয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ পাশ করে সরকার জনসাধারণ এবং গণমাধ্যমের প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রাপ্তির দাবি ও চাহিদা মেটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সংসদের কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন ও গণমানুষের কাছে এর কার্যক্রম প্রচার প্রসারের জন্য ‘সংসদ টেলিভিশন’ চালু করা হয়েছে। ব্যবসার ক্ষেত্রে একাধিপত্য রোধকল্পে ব্যবসায় ‘প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২’ প্রণয়ন করা হয়েছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটগণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে বিচারকার্যে শুদ্ধাচার অনুশীলনকে জোরদার করা হয়েছে। সরকার দুর্নীতির মামলাসমূহ পরিচালনাকে ত্বরান্বিত ও জোরদার করেছে; পৃথক ‘প্রসিকিউশন উইং’ প্রতিষ্ঠা করেছে। সরকারি কর্মকর্তাদের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) আয়কর প্রদান ও সম্পত্তির হিসাব প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতাকে জোরদার করার জন্য নিজস্ব কর্মকতা-কর্মচারী নিয়োগ ও আর্থিক স্বনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসনেও প্রভূত সংস্কার সাধিত হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পদ্ধতিগত সংস্কার সাধন করেছে এবং নতুন আইন প্রণয়ন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাদের সংশোধন আনয়ন করেছে। নবম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনে (জুন, ২০১২) পাশকৃত ১৮০টি আইনের মধ্যে উল্লিখিত আইনসমূহ ছাড়াও দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত উল্লেখযোগ্য আইন ও নীতি হল: ‘সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯’, ‘ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯’, ‘জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯’, ‘আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) আইন, ২০১০’, ‘সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯’, ‘চার্টার্ড সেক্রেটারিজ আইন, ২০১০’, ‘পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০’, ‘পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ ‘মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২’, ‘জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০, ইত্যাদি।
১.৪ শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নের যৌক্তিক ভিত্তি
(ক) তত্ত্বগতভাবে বলা চলে যে, উল্লিখিত আইনকানুন ও প্রথা-পদ্ধতি এবং উন্নয়ন উদ্যোগ দুর্নীতি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে এবং তা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞতা হতে প্রতীয়মান হয় যে, সুষ্ঠু প্রয়োগের অভাবে এগুলির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাচ্ছে না। বিভিন্ন আইন ও কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনও এখানে বড় বাধা। রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে এগুলির মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন। অতীতে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রম এত বিশাল এবং বিপুল ছিল না; সম্প্রতি কেবল সরকারি খাতই নয়, এনজিও খাত ও বেসরকারি খাতেও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের বিপুল প্রসার ঘটেছে। এ সকল কর্মকাণ্ডে বিপুল পরিমাণ সম্পদের সংশ্লিষ্টতা ঘটছে এবং পূর্বেকার সাংগঠনিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতি এবং লোকবলের মাধ্যমে তাদের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন কষ্টকর হয়ে পড়ছে; সরকারি-ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকজনের দুর্নীতির সুযোগও বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি, সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের কারণে লোকজনের মধ্যে দুর্নীতির প্রবণতাও বাড়ছে বলে প্রতীয়মান হয়। পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম জোরদার করেছে; এরই সমন্বিত প্রচেষ্টা হিসাবে এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার সকল উদ্যোগের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই শুদ্ধাচার কৌশলটি প্রণয়ন করা হয়েছে।
(খ) প্রথম ও দ্বিতীয় ‘দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে’ দুর্নীতিকে উন্নয়নের একটি প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং এর প্রতিকারমূলক উদ্যোগের বিষয় বিবেচনা করা হয়েছিল। চলমান ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (অর্থ-বছর ২০১১-২০১৫) সুশাসন ও দুর্নীতি দমনকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। দলিলটিতে ‘দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ’ শিরোনামের উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, ‘‘সরকার দুর্নীতি সুরাহা করার গুরুত্ব স্বীকার করে এবং অধিকতর হারে ‘ই-গভর্নেন্স’ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, ‘সিটিজেন চার্টার’ প্রণয়ন করে নাগরিকগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটিয়ে, সরকারের কর্মকাণ্ডকে অধিকতর স্বচ্ছ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার প্রদানের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করে দুর্নীতির সুযোগ হ্রাস করার লক্ষ্যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।’’ ‘রূপকল্প ২০২১’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত ‘বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১’ দুর্নীতি দমনের উদ্যোগকে একটি আন্দোলন হিসাবে অভিহিত করে সরকারি কাজে ‘জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা’, ‘স্বচ্ছ সংগ্রহ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা’, ‘নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উন্নয়ন সাধন’, ‘কার্যকর ন্যায়পাল’ প্রতিষ্ঠা, এবং ‘আইনশৃঙ্খলা’ পদ্ধতির উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। দুর্নীতিবিরোধী এই আন্দোলন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উল্লিখিত পরিকল্পনাসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেইসঙ্গে একটি সমন্বিত ও সংহত পরাকৌশল অনুসরণ করা হলে দুর্নীতি দমন অধিকতর কার্যকর হবে বলে প্রতীয়মান হয়।
(গ) সরকারি দফতর ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার অতি সহজে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ভূমি রেকর্ড, পুলিশের সাধারণ ডায়েরি, কারখানার মূল্য সংযোজনের হিসাব, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বা পরীক্ষার বিষয়, এ সকল ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার দুর্নীতি উৎপাটন করতে সক্ষম। সরকার তাই মনে করে যে, সরকারি দফতরে অথবা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম এবং অনেকে ক্ষেত্রে তা সম্ভব করে তুলেছে। সেজন্য সরকার ব্যাপকভাবে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার দ্রুতায়িত করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।
(ঘ) স্বাধীনতা লাভের গোড়া থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের গৃহীত সকল নীতি ও কনভেনশনের প্রতি অব্যাহতভাবে সমর্থন প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত আছে যে, ‘ ... আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা – এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি...।’। জাতিসংঘের United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) জাতিসংঘের একটি উল্লেখযোগ্য কনভেনশন এবং বাংলাদেশ তা অনুসমর্থন করেছে। উল্লিখিত কনভেনশনটিতে দুর্নীতি নির্মূলের জন্য ‘ফৌজদারি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ, আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে দুর্নীতির প্রতিকার ছাড়াও দুর্নীতির ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণকে’ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই কনভেনশনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ‘প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্র তার আইন-ব্যবস্থার মৌলিক নীতিমালা অনুযায়ী কার্যকর এবং সমন্বিত দুর্নীতিবিরোধী নীতি প্রণয়ন করবে যা সমাজের অংশগ্রহণকে উন্নত করবে এবং আইনের শাসন, জনসম্পদ এবং জনসংযোগের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা, সততা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি-নীতির প্রতিফলন ঘটাবে।’ (অনুচ্ছেদ ৫.১)। এই প্রেক্ষাপটে শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। এ কনভেনশন বাস্তবায়নের বিষয়ে জাতিসংঘে প্রদত্ত বাংলাদেশ সরকারের প্রতিবেদনে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ‘বিবিধ অভ্যন্তরীণ পদ্ধতিগত দুর্বলতার সুযোগেই দুর্নীতির প্রসার ঘটে।’ পদ্ধতিগত সেসব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধকে একটি কার্যকর ও গতিশীল আন্দোলন হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কৌশল-দলিল হিসাবে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার উৎসাহিতকরণের ক্ষেত্রে অব্যাহত কার্যক্রমের প্রতিনিধিত্বমূলক দলিল হিসাবে সরকার এই ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ প্রণয়ন করছে।
[[[১.৫ জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থা
(ক) সমাজ ও রাষ্ট্রে দুর্নীতি নির্মূল ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রাষ্ট্র আইনকানুন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে তাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, সমাজ তা প্রতিপালন করে; সেইসঙ্গে সমাজের নীতিচেতনা ও মূল্যবোধও রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হয়। এই সম্পর্কের জটাজালে ব্যক্তিমানুষের নৈতিকতা ও শুদ্ধতার উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠা যেমন প্রয়োজন, তেমনি তার যুক্তরূপ প্রতিষ্ঠানগত শুদ্ধাচার উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠাও জরুরি। এই কৌশলটির চূড়ান্ত লক্ষ্য ব্যক্তিমানুষের শুদ্ধাচার, অন্য কথায় চরিত্রনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা; কিন্তু এর হাতিয়ার হিসাবে প্রতিষ্ঠানকে বেছে নেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র, বেসরকারি ব্যবসা খাত ও সুশীল সমাজের যেসব প্রতিষ্ঠান শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে প্রতীয়মান হয়, তাদের উন্নয়ন বিবেচনা করা হয়েছে; শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-নীতির উন্নয়ন সাধন, ক্ষেত্রবিশেষে আইন ও পদ্ধতির পরিবর্তন এবং নতুন আইন ও পদ্ধতি প্রবর্তন, লোকবলের দক্ষতার উন্নয়ন, এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কার্যকারিতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে এ দলিলটিতে।
(খ) একজন মানুষের নৈতিকতা শিক্ষা শুরু হয় পরিবারে এবং শুদ্ধাচার অনুসরণের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। তার পরের ধাপে আছে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান; নৈতিক জীবন গড়ার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অপরিসীম। এ প্রেক্ষাপটে শুদ্ধাচারের কৌশলে এগুলির ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। সরকারের নির্বাহী বিভাগের জনপ্রশাসন ও স্থানীয় সরকারসমূহ সরকারি কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। এসব প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা, এবং এগুলিতে নিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠাই কৌশলটির মূল লক্ষ্য। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ তিনটি অঙ্গে বিভক্ত – আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগ। তারা স্বাধীন সত্তায় তাদের কর্মবৃত্তে যথাক্রমে রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন, নির্বাহীকার্য ও বিচারকার্য পরিচালনা করে। সংবিধান অনুযায়ী গঠিত আরও কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন, নির্বাচন কমিশন, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, সরকারি কর্ম কমিশন, ন্যায়পাল বাজেট ও আর্থিক নিয়মাবলি পালন সাপেক্ষে স্বাধীনভাবে কর্মসম্পাদনে ক্ষমতাবান। অন্য আরও কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা আলাদা আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট এবং ‘সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ’ হিসাবে অভিহিত। যেমন, দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, ইত্যাদি। সংবিধানে স্থানীয় শাসনের যে-ব্যবস্থা নির্দেশ করা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম ও শহরের স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান যেমন, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন সৃষ্টি করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানের সকলের ভূমিকাকেই বিবেচনা করা জরুরি। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যেমন অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে তেমনই রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ ও এনজিও এবং ব্যক্তিখাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সাকুল্যে অরাষ্ট্রীয় হিসাবে চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সার্বিক বিচারে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে:
(অ) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান
- নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন
- জাতীয় সংসদ
- বিচার বিভাগ
- নির্বাচন কমিশন
- অ্যাটর্নি জেনারেল
- সরকারি কর্ম কমিশন
- মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
- ন্যায়পাল
- দুর্নীতি দমন কমিশন
- স্থানীয় সরকার
(আ) অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান
- রাজনৈতিক দল
- বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান
- এনজিও ও সুশীলসমাজ
- পরিবার
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
- গণমাধ্যম
(গ) এই কৌশলটি প্রণয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান দলিলপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে; বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন, সুশীল সমাজ ও নাগরিকগোষ্ঠীর সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরামর্শসভা আয়োজন করে তাদের মতামত বিবেচনা করা হয়েছে; মাননীয় সংসদ সদস্য ও অন্যান্য অংশীজনের প্রদত্ত অভিমত গ্রহণ করা হয়েছে। জনমত যাচাইয়ের জন্য খসড়া কৌশলপত্রটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করা হয়েছিল এবং তাতে প্রাপ্ত মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। কৌশলপত্রটি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের লিখিত মতামতও গ্রহণ করা হয়েছে। খসড়াটি পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রিসভা কর্তৃক গঠিত মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন কমিটি কয়েকটি সভায় মিলিত হয়ে দলিলটির কাঠামো ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে যেসব মতামত প্রকাশ ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন তার আলোকে সার্বিকভাবে এই দলিলটি বিন্যস্ত করা হয়েছে। এই কৌশলপত্রটি দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচারের চূড়ান্ত দলিল নয়; সময়ে সময়ে এটি পর্যালোচিত হবে এবং এর উন্নয়ন সাধন করা হবে – এই ধারণার আলোকেই এই দলিলটি প্রণয়ন করা হয়েছে।
- রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য (Vision and Mission)
রূপকল্পঃ সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা।
অভিলক্ষ্যঃ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা।
অধ্যায় ২
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল — রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান
এই কৌশলপত্রটিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এর প্রেক্ষাপট ও চ্যালেঞ্জ বর্ণনা করা হয়েছে এবং লক্ষ্য, সুপারিশ ও কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদ প্রস্তাব হয়েছে: এ মেয়াদসমূহ যথাক্রমে এক বছর, তিন বছর এবং পাঁচ বছর।
২.১ নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন
২.১.১ প্রেক্ষাপট
(ক) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা, স্থানীয় শাসনব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ ও অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর এবং মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, দপ্তর, সংবিধিবদ্ধ ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা নিয়ে নির্বাহী বিভাগ গঠিত। নির্বাহী বিভাগের বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে জনপ্রশাসন। সরকারি কর্মকাণ্ডের একটি বৃহৎ অংশ এই বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে এবং শুদ্ধাচার প্রতিপালনের ক্ষেত্রে এই বিভাগ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। নির্বাহী বিভাগ রাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গ, যেমন, আইনসভা ও বিচার বিভাগ এবং অন্যান্য সাংবিধানিক সংস্থার স্বাধীনতা সুরক্ষা করে এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে। শুদ্ধাচার পালনার্থে প্রণীত ও প্রতিষ্ঠিত আইনকানুন, সংসদ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং বিচার বিভাগের কাছে জবাবদিহির মাধ্যমে এই বিভাগে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ শুদ্ধাচার পালন করেন।
(খ) জনপ্রশাসনে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ যাতে স্বচ্ছতা ও নিয়মনিষ্ঠা পালন করে এবং দলীয় প্রভাব ও হস্তক্ষেপের ঊর্ধ্বে থেকে নাগরিকদের সেবা প্রদান করতে সক্ষম হয় তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। সেই লক্ষ্যে স্বাধীনতার পর থেকে জনপ্রশাসনে প্রভূত সংস্কার সাধন করা হয়েছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ক্যাডার ও সার্ভিসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে; পরবর্তী পর্যায়ে জনপ্রশাসনকে ঊনত্রিশটি ক্যাডার সার্ভিসে বিন্যস্ত করা হয়েছে; কর্মকর্তা কর্মচারীদের কৃতি মূল্যায়নে এবং পদোন্নতি প্রদানে নতুন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, আর্থিক পারিতোষিক বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সংস্কার সাধন করা হয়েছে। জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বক্ষেত্রেই ‘আচরন বিধি’ ও ‘সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপীল বিধি’ প্রযুক্ত হয়। সরকারি কর্মকর্তাগণকে বর্তমানে ‘আয়কর আইনের’ বিধান অনুসারে আয়কর ও সম্পদের হিসাব প্রদান করতে হয়। দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যপরিধি সম্পূর্ণ জনপ্রশাসনে ব্যাপ্ত। জনপ্রশাসনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর দুর্নীতির বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান পরিচালনা করে অভিযোগ দায়ের ও মামলা পরিচালনা করে। দুর্নীতির বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি দমন বিষয়ক পাঠক্রম অনুসৃত হচ্ছে।
(গ) বর্তমান সরকারের আমলে জনপ্রশাসনের বিপুল কর্মযজ্ঞে দক্ষতা আনয়ন, দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রভূত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। বিগত সাড়ে তিন বছরে সরকার নিয়ম-নীতি, পদ্ধতি ও আইনকানুনের সংস্কার সাধন করে সুশাসনকে জোরদার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। নতুন আইন প্রণয়ন, তাদের সংস্কার ও পদ্ধতিগত উন্নয়নের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: বাজেট ও পরিকল্পনা খাতে ‘সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ প্রণয়ন’; ‘সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতাভুক্তকরণ’; ‘কর্মকৃতিভিত্তিক নিরীক্ষা কার্যক্রম’ চালুকরণ; আর্থিক খাতে ‘মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২’ প্রণয়ন; ‘সন্ত্রাসবিরোধী আইন (সংশোধন) ২০১২’ প্রণয়ন; ‘সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক ইস্যু) বিধিমালা, ২০০৬’ সংশোধন; শিক্ষা খাতে ‘শিক্ষা নীতি’ জারি; স্বাস্থ্য খাতে ‘স্বাস্থ্য নীতি’ জারি; শিল্পায়ন উদ্যোগের ক্ষেত্রে ‘শিল্প নীতি ২০১০’ অনুমোদন, ‘ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯’ প্রণয়ন; জলবায়ু ও পরিবেশ খাতে ‘বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন ২০১০’ জারি; ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ‘জাতীয় আইসিটি আইন, ২০০৯ ও আইসিটি নীতিমালা, ২০০৯’ প্রণয়ন, সকল ধরনের সরকারি ক্রয়ের জন্য e-procurement ও e-monitoring ব্যবস্থা চালুকরণ; নারী ও শিশুকল্যাণ খাতে ‘জাতীয় শিশুশ্রম নীতি, ২০১০’ জারি; সুশাসনের ক্ষেত্রে ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ প্রণয়ন; ‘জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন, ২০১১’ প্রণয়ন; ‘সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১’ প্রণয়ন; ‘মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২’ প্রণয়ন; ‘নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০১০’ প্রণয়ন; ‘জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯’ প্রণয়ন, ইত্যাদি। এসব আইন ও ব্যবস্থা সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে প্রভূত অবদান রাখছে।
(ঘ) নীতি বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং তাদের দক্ষতার উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনপ্রশাসনকে অধিকতর স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও দুর্নীতিমুক্ত করার লক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব অধিকতর নিবিড়ভাবে মনিটর করা প্রয়োজন। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মমূল্যায়ন, পদোন্নতি প্রদান, কর্মজীবন সোপানের অগ্রগতি সাধন, প্রণোদনা প্রদানে অধিকতর সুষ্ঠুতা আনয়ন এবং পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটের সঙ্গে এগুলির সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন। জনপ্রশাসনে আইনকানুন, বিধিবিধানে পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করে একে অধিকতর যুগোপযোগী করে তোলার মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার নিশ্চিত করাও জরুরি। কিছু কিছু সমস্যা জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে; যেমন, ভূমি মালিকানা ও অধিকারিত্বের ক্ষেত্রে আইনের দুর্বল প্রয়োগ, ভূমি ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি, ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেচ্ছাচার, ভেজাল খাবার ও পণ্যের প্রসার, ইত্যাদি। সুশাসন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে কঠোরভাবে আইন ও বিধিবিধান প্রয়োগ এবং নতুন কিছু আইন ও নীতি প্রণয়ন জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে।
২.১.২ চ্যালেঞ্জ
এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:
- সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন;
- উন্নততর দায়বদ্ধতাসহ কর্ম সম্পাদনে পাবলিক সার্ভিসের অধিকতর স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ;
- প্রশাসনিক কর্মপ্রক্রিয়ায় অধিকতর দক্ষতা ও কার্যকারিতা আনয়ন;
- নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি, বদলি ও প্রণোদনামূলক পারিতোষিকের সঙ্গে সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়নের সংযোগ সাধন;
- অন্যান্য খাতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিযোগিতামূলক বেতন ও সুবিধা-কাঠামো প্রতিষ্ঠা;
- বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যে সুযোগের অধিকতর সামঞ্জস্য বিধান করে পাবলিক সার্ভিসের সামগ্রিক সংস্কার সাধন;
- সুস্পষ্টভাবে বিধৃত প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলি (যেমন আইন প্রয়োগ ও তদন্ত) নিশ্চিত করে অধিকতর নাগরিকবান্ধব আইনশৃঙ্খলা বাহিনী গড়ে তোলা;
- জনপ্রশাসনে (বিশেষত পদোন্নতি, বদলি, বৈদেশিক নিয়োগ, ইত্যাদিতে) দৃষ্টিগ্রাহ্য নিরপেক্ষতা অবলম্বনে অধিকতর মেধাবী ও যোগ্য কর্মকর্তাদের নিয়োগের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
২.১.৩ লক্ষ্য ও সুনির্দিষ্ট সুপারিশ
লক্ষ্য
জনগণের চাহিদা ও দাবির প্রতি দ্রুত সাড়া দানে সক্ষম, এবং জনগণ ও সংসদের নিকট দায়বদ্ধ, স্বচ্ছ নির্বাহী বিভাগ প্রতিষ্ঠা।
স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ
- প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে জনপ্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদ-বিবরণী নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট জমাদানের ব্যবস্থা করা;
- বেআইনি কাজ ও অসদাচরণ সম্পর্কে তথ্য-প্রদানকারী ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য ‘জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন’ বাস্তবায়ন;
- পাবলিক সার্ভিসে grievance redress system-এর আওতায় অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন;
- একটি আধুনিক বার্ষিক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থার প্রবর্তন;
- প্রতি বছর নিয়মিতভাবে শূন্য পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিশ্চিত করা।
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ
১. পাবলিক সার্ভিসের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের জন্য সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন;
২. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ‘কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা’ প্রণয়নের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দায়বদ্ধ, যোগ্য ও দ্রুত
সাড়াদান- সক্ষম নির্বাহী বিভাগ প্রতিষ্ঠা;
৩. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য কর্মকালীন প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা
বৃদ্ধিকরণ;
৪. জ্যেষ্ঠতা, কৃতি, জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পদোন্নতি পদ্ধতি প্রবর্তন;
৫. সরকারি সেবায় কার্যকারিতা আনয়ন ও গণমানুষের কাছে তা দ্রুত ও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ই-গভর্নেন্স প্রবর্তন ও
তার প্রসার;
৬. সরকারি কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জন্য যৌক্তিক বেতন কাঠামো নির্ধারণ ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে
সামঞ্জস্য বিধান করে এগুলির সমন্বয় সাধন।
২.১.৪ কর্মপরিকল্পনা
|
ক্রমিক |
কার্যক্রম |
কর্মসম্পাদন সূচক |
সময় |
দায়িত্ব |
সহায়তাকারী |
|---|---|---|---|---|---|
|
১. |
সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন |
সিভিল সার্ভিস আইন প্রণীত |
মধ্যমেয়াদে |
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় |
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ |
|
২. |
‘কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা’ প্রণয়ন |
কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত ও অনুসৃত; পদোন্নতিতে স্বচ্ছতা ও যৌক্তিক নীতিমালা অনুসৃত
|
মধ্যমেয়াদে |
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় |
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
|
৩. |
অংশগ্রহণমূলক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন |
নতুনভাবে গৃহীত মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসৃত |
স্বল্পমেয়াদে |
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় |
সকল মন্ত্রণালয় |
|
৪. |
বিধানানুসারে আয় ও সম্পদের বিবরণ নিয়মিতভাবে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কাছে জমাদান |
জমাকৃত বিবরণী-প্রতিবেদন |
স্বল্পমেয়াদে |
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় |
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ |
|
৫. |
সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জন্য উন্নততর বেতন, ও সুবিধাদি প্রদান |
স্থায়ী বেতন ও সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠিত |
দীর্ঘমেয়াদে |
অর্থ বিভাগ |
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
|
৬. |
ই-গভর্নেন্স প্রবর্তনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা |
ক) সকল মন্ত্রণালয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রচলন এবং ব্যবহার; (খ) ই-গভর্নেন্স-এর মাধ্যমে লব্ধ সরকারি সেবার সংখ্যা ও মান বৃদ্ধি |
স্বল্পমেয়াদে |
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় |
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
|
৭. |
অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন |
সরকারি দপ্তরসমূহে অভিযোগ ব্যবস্থাপনার জন্য ‘ফোকাল পয়েন্ট’ নির্ধারিত এবং জনসাধারণ সে-সম্পর্কে অবহিত |
স্বল্পমেয়াদে |
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
সকল মন্ত্রণালয় |
|
৮. |
মন্ত্রণালয়সমূহের গুচ্ছ (cluster) গঠন |
গুচ্ছ গঠিত ও গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত |
দীর্ঘমেয়াদে |
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
|
সকল মন্ত্রণালয় |
|
৯. |
‘জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা ) আইন, ২০১১ প্রণয়ন’ |
গেজেটে আইন প্রকাশিত |
বাস্তবায়িত |
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ |
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
|
১০. |
মামলা তদন্তে পৃথক তদন্ত বিভাগ প্রবর্তন করা |
গেজেটে আইন প্রকাশিত |
স্বল্পমেয়াদে |
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় |
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; অর্থ বিভাগ |
|
১১. |
ভূমি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন |
ভূমি ব্যবস্থায় ‘ডিজিটাইজড্’ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত। |
মধ্যমেয়াদে |
ভূমি মন্ত্রণালয় |
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় |
|
১২. |
কঠোরভাবে খাদ্য ও পণ্যের ভেজাল প্রতিরোধ |
ভেজাল প্রতিরোধ আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন |
স্বল্পমেয়াদে এবং অব্যাহতভাবে |
বিএসটিআই |
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় |
২.২ জাতীয় সংসদ
২.২.১ প্রেক্ষাপট
(ক) স্বাধীনতার পর হতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতিশাসিত, উভয় প্রকার সরকার প্রত্যক্ষ করেছে। ১৯৯১ সাল থেকে বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার চালু আছে এবং ২০০৯ সাল থেকে নবম সংসদ কার্যকর ‘দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান’ হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে। এই সংসদের প্রথম অধিবেশনেই নির্ধারিত সংসদীয় কমিটিসমূহ গঠন করা হয়েছে এবং সেগুলিতে সরকার ও বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যগণের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। কমিটিসমূহের সভা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং আলোচিত বিষয় সম্পর্কে সর্বসাধারণকে নিয়মিতভাবে অবহিত করা হয়।
(খ) জাতীয় সংসদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এবং সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি অনুযায়ী মৌলিক দায়িত্ব হিসাবে অব্যাহতভাবে আইন প্রণয়ন, নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রম তদারকি, তত্ত্বাবধান ও প্রতিনিধিত্বমূলক কার্য সম্পাদন করছে। সংসদ সদস্যগণ সক্রিয়ভাবে আইনপ্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছেন এবং সরকারি হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সরকারের ‘বার্ষিক আর্থিক হিসাব’ ও ‘নির্দিষ্টকরণ হিসাব’ এবং তৎসম্পর্কিত মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের রিপোর্ট ও তৎপ্রণীত অন্যান্য রিপোর্ট পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরের কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করছেন। স্বাধীনভাবে নির্বাহী বিভাগের ভূমিকা পর্যালোচনা, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের কার্যসম্পাদন, সংক্রিয়ভাবে প্রশ্নোত্তর-পর্ব পরিচালনা এবং অন্যান্য কার্যের মাধ্যমে সংসদ প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীবৃন্দের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করছে। সংসদীয় কমিটিসমূহ এখন অধিকতর তৎপর হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য তারা মাঠ পর্যায়েও বৈঠক করছে। সংসদ সদস্যগণের এবং স্থায়ী কমিটিসমূহের সাচিবিক চাহিদা পূরণে জাতীয় সংসদ সচিবালয় অধিকতর সক্ষমতা অর্জন করেছে। সংসদ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে সংসদের অধিবেশনসমূহ ‘সংসদ টেলিভিশন’-এর মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। জাতীয় সংসদ ও সংসদ সচিবালয়ের সকল কার্যক্রমকে ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনয়নের মাধ্যমে ‘ডিজিটাল পার্লামেন্ট’ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
(গ) সর্ববিষয়ে সরকারি ও বিরোধী দলীয় সদস্যগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই কেবল জাতীয় সংসদ ‘দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান’ হিসাবে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হতে পারে। বর্তমানে (২০১২ সালে) প্রধান বিরোধী দলের সংসদ সদস্যগণ কমিটি-কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলেও নিয়মিত অধিবেশনে যোগদান থেকে বিরত রয়েছেন। সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা পালনার্থে নিয়মিত অধিবেশনে সকল দলের সংসদ সদস্যগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
২.২.২ চ্যালেঞ্জ
এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:
- জাতীয় সংসদ ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে উন্নততর দায়বদ্ধতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা;
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের উন্নততর তত্ত্বাবধানকার্য সম্পাদন;
- কার্যকর ‘ফাইনেনসিয়াল ওভারসাইট কমিটি’ (সরকারি হিসাব কমিটি, সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি, অনুমিত হিসাব কমিটি) গঠন, তাদের পরীক্ষণ ও তদারকি কার্য সম্পাদন;
- সংসদের নিয়মিত অধিবেশনে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
- সংসদ সদস্য ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহকে উন্নততর লজিস্টিক সহায়তা প্রদান।
২.২.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ
লক্ষ্য
সংসদে আইন প্রণয়ন ও সরকারের কার্যক্রম তদারকির (oversight) মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহতকরণ।
স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ
- কার্যপ্রণালী-বিধির আওতায় প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীবৃন্দ এবং বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদের জন্য যৌক্তিক সময় নিশ্চিতকরণ;
- সংসদ সদস্যবর্গ ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের (ক) আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া, (খ) সংসদীয় কমিটিসমূহের কার্যনির্বাহ, ও (গ) বাজেট প্রক্রিয়ায় সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সরকারের ‘বার্ষিক আর্থিক হিসাব’ ও সরকারের ‘নির্দিষ্টকরণ হিসাব’ তৎসম্পর্কিত মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের রিপোর্ট ও তৎপ্রণীত অন্যান্য রিপোর্ট পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরের কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান জোরদারকরণ;
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ
- সংসদের অধিবেশনে বিরোধী দলের নিয়মিত অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
- সংসদের প্রথম অধিবেশনেই বিভিন্ন দলের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠনের রীতি অব্যাহত রাখা;
- প্রণীতব্য আইন কার্যকরভাবে পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকল্পে সংসদ কর্তৃক স্থায়ী কমিটিসমূহকে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত প্রদান নিশ্চিতকরণ; সেইসঙ্গে কার্যপ্রণালি বিধির আওতায় বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করে কমিটিসমূহকে শক্তিশালীকরণ;
- জাতীয় সংসদকে অধিকতর দক্ষ ও কার্যকর করার জন্য যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান।
২.২.৪ কর্মপরিকল্পনা
|
ক্রমিক |
কার্যক্রম |
কর্মসম্পাদন সূচক |
সময় |
দায়িত্ব |
সহায়তাকারী |
|---|---|---|---|---|---|
|
১. |
সংবিধান ও কার্যপ্রণালী-বিধি অনুযায়ী সংসদের প্রথম অধিবেশনে বিরোধী দলসমূহের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সংসদীয় কমিটিসমূহ গঠন অব্যাহত রাখা |
ভবিষ্যৎ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম অধিবেশনে সকল সংসদীয় কমিটি গঠন সম্পন্ন করা |
সংসদের প্রথম অধিবেশন চলাকালে |
স্পীকার; সংসদ নেতা |
রাজনৈতিক দলসমূহের সংসদ নেতা; সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা |
|
২. |
বিরোধী দলীয় সদস্যগণের সংসদের অধিবেশনে নিয়মিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ |
সংসদ অধিবেশনে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যগণের নিয়মিত অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আইনি সংস্কার সাধিত; নিয়মিত উপস্থিতির সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত |
চলমান ও দীর্ঘমেয়াদে |
স্পীকার; সংসদ নেতা |
সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা |
|
৩. |
প্রধানমন্ত্রী/ মন্ত্রীগণের প্রশ্নোত্তর পর্বে কার্যপ্রণালি-বিধির আওতায় বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যসহ সকল সদস্যের জন্য যৌক্তিক সময় বরাদ্দকরণ |
প্রধানমন্ত্রী/ মন্ত্রীগণের প্রশ্নোত্তর পর্বে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যগণের বর্ধিত হারে অংশগ্রহণ |
চলমান |
স্পীকার |
মন্ত্রীবৃন্দ |
|
৪. |
সংসদ সদস্যগণের সম্পদের বিবরণ জনসমক্ষে প্রকাশের ব্যবস্থা প্রবর্তন |
সংসদের প্রথম অধিবেশনে সম্পদ-বিবরণী সংক্রান্ত তথ্য সর্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত |
দীর্ঘমেয়াদে |
স্পীকার |
সংসদ সদস্যবৃন্দ; সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলীয় নেতৃবৃন্দ |
|
৫. |
সংবিধান ও কার্যপ্রণালি বিধিতে নির্ধারিত দায়িত্বের ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে সরকারি হিসাব কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠান |
অব্যাহতভাবে অনুসৃত |
চলমান; সকল অধিবেশন |
সরকারি হিসাব কমিটি |
|
|
৬. |
সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের নিয়মিত বৈঠক অব্যাহত রাখা |
মাসিক বৈঠক অনুষ্ঠান, সুপারিশ প্রদান ও অব্যাহত অনুসরণ |
চলমান |
স্থায়ী কমিটির সভাপতিবৃন্দ |
স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ; মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক; সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় |
|
৭. |
বাজেট প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ এবং ‘ফাইনেনশিয়াল ওভারসাইট’ কমিটিসমূহের বৈঠক অনুষ্ঠানের বিষয়ে সংসদ সদস্যবৃন্দ ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি |
সংসদ সচিবালয়ের বাজেট পর্যবেক্ষণ ইউনিট চালু; সংসদ সদস্য ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা আয়োজিত |
চলমান |
জাতীয় সংসদ সচিবালয় |
অর্থ মন্ত্রণালয়; পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক |
|
৮. |
জনবল, সরঞ্জাম, অফিস সংস্থানের মাধ্যমে স্থায়ী কমিটিসমূহকে সহায়তা প্রদান |
স্থায়ী কমিটিসমূহের চাহিদা অনুযায়ী জনবল, সরঞ্জাম ও অফিস প্রাপ্তি |
চলমান |
জাতীয় সংসদ সচিবালয় |
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; অর্থ বিভাগ |
|
৯. |
জাতীয় সংসদ ও সংসদীয় কার্যপদ্ধতিতে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার |
ই-সংসদ প্রবর্তিত; সকল আইন, বিধি, নীতি এবং সার্কুলার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ও আর্কাইভে সংরক্ষিত |
চলমান |
জাতীয় সংসদ সচিবালয় |
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়; অর্থ বিভাগ |
|
১০ |
জনগণের প্রতি সংসদ সদস্যগণের দায়িত্ব ও জবাবদিহি নিশ্চিতকল্পে তাঁদের জন্য একটি আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রতিপালন |
জাতীয় সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণবিধি প্রণীত ও নিয়মিতভাবে প্রতিপালিত |
দীর্ঘমেয়াদে |
জাতীয় সংসদ |
|
|
১১. |
জাতীয় সংসদের পিটিশন কমিটিকে অধিকতর কার্যকর করা |
পিটিশন কমিটির বৈঠক নিয়মিত অনুষ্ঠিত |
চলমান |
জাতীয় সংসদ |
|
২.৩ বিচার বিভাগ
২.৩.১ প্রেক্ষাপট:
(ক) আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং সেইসঙ্গে অধস্তন আদালতসমূহ ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল নিয়ে বিচার বিভাগ গঠিত। রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির নিয়োগদান করেন এবং তাঁর সঙ্গে পরামর্শক্রমে আপীল ও হাইকোর্ট বিভাগের অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করেন; রাষ্ট্রপতি অধস্তন আদালতের জন্য প্রণীত বিধি অনুযায়ী বিচার বিভাগীয় পদ বা বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট পদেও নিয়োগদান করেন। বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে। সংবিধানে উল্লেখ আছে যে, ‘এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারক বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।’ আইনসভা কর্তৃক প্রণীত এবং বিদ্যমান আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করা এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও আইনের শাসন সমুন্নত রাখা বিচার বিভাগের দায়িত্ব।
(খ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই বিভাগের বিন্যাস ও কর্মপরিধিতে প্রভূত পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। ২০০৭ সালের ১লা নভেম্বর ‘জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসি’-কে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাহী বিভাগ হতে সম্পূর্ণ পৃথক করা হয়েছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আইন ২০১১ অনুযায়ী সংবিধানের ১১৬ক অনুচ্ছেদবলে ‘বিচার কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচারকার্যে স্বাধীন থাকিবেন’ মর্মে নিশ্চিত করা হয়েছে। তাঁদের ‘নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরিসহ) ও শৃঙ্খলাবিধান’ রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। শারীরিক ও মানসিক অসামর্থ্য ও গুরুতর অসদাচরণের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের অপসারণ সুপারিশ করার জন্য সংবিধানে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠনের ব্যবস্থা আছে।
(গ) বাংলাদেশের একজন প্রধান বিচারপতি তাঁর সম্পদের হিসাব জমা দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন; এর অনুসরণ শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় প্রভূত সহায়ক হতে পারে। বিচারকগণের সুষ্ঠু নিয়োগ, বিচারিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর আর্থিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান, সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রবর্তন এবং সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রারের দপ্তর অধিকতর শক্তিশালীকরণ, বিচার ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে প্রতীয়মান হয়। মামলা-মোকদ্দমার জট নিরসনও অত্যন্ত জরুরি।
২.৩.২ চ্যালেঞ্জ
এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:
- স্বচ্ছ নিয়োগ পদ্ধতি প্রবর্তন;
- বিচার বিভাগের অধিকতর আর্থিক স্বায়ত্তশাসন;
- বিচারকগণের দায়বদ্ধতা অধিকতর দৃশ্যমান করা;
- নতুন বিষয়ে প্রণীত আইনের ক্ষেত্রে (যেমন, ‘মানি লন্ডারিং’) উন্নততর তথ্য-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;
- বিচার বিভাগ সম্পর্কে জনগণের ধারণা উজ্জ্বলতর করা;
- বিচারক-মামলা অনুপাতের উন্নয়ন সাধন;
- যৌক্তিক সময়ে মামলার নিষ্পত্তি।
২.৩.৩ লক্ষ্য ও সুনির্দিষ্ট সুপারিশ
লক্ষ্য
রাষ্ট্রের একটি স্বাধীন, কার্যকর ও নিরপেক্ষ অঙ্গ হিসাবে বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠা লাভ।
স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ
- জুডিশিয়াল কর্মকর্তাদের আচরণবিধির যথাযথ বাস্তবায়ন;
- সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রারের কার্যালয়কে শক্তিশালীকরণ।
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ
- সুপ্রীম কোর্টে বিচারক নিয়োগের লক্ষ্যে আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়ন;
- নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অনুসারে বিধি প্রণয়ন এবং যোগ্যতার মানদণ্ডের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ;
- বিচারিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক্স, সরঞ্জাম ও লোকবল প্রদান;
- অব্যাহতভাবে বিচারকগণের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের আয়োজন করা;
- মামলার জট হ্রাসকরণ;
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ।
২.৩.৪ কর্মপরিকল্পনা
|
ক্রমিক |
কার্যক্রম |
কর্মসম্পাদন সূচক |
সময় |
দায়িত্ব |
সহায়তাকারী |
|
১. |
সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগের উদ্দেশ্যে মনোনয়নের জন্য আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়ন |
আইন/বিধিমালা/ নীতিমালা প্রণীত |
মধ্যমেয়াদে |
আইন ও বিচার বিভাগ |
সুপ্রীম কোর্ট |
|
২. |
বিধানানুসারে বৎসরান্তে বিচারক ও কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব-বিবরণী নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট জমাদান |
সম্পদের হিসাব-বিবরণী জমাদান এবং তৎসম্পর্কিত প্রতিবেদন |
মধ্যমেয়াদে |
আইন ও বিচার বিভাগ |
সুপ্রীম কোর্ট |
|
৩. |
সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের ফলপ্রসূ কার্যনির্বাহের জন্য পদ্ধতি, নীতি ও কার্যপ্রণালি প্রণয়ন ও তাদের বাস্তবায়ন |
সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের পদ্ধতি, নীতি, কার্যপ্রণালি প্রণীত |
স্বল্পমেয়াদে |
আইন ও বিচার বিভাগ |
সুপ্রীম কোর্ট |
|
৪. |
বিচারকগণের সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা এবং বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট শক্তিশালীকরণ |
প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রতিবেদন |
স্বল্পমেয়াদে ও অব্যাহতভাবে |
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট; আইন ও বিচার বিভাগ |
সুপ্রীম কোর্ট; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; অর্থ বিভাগ |
|
৫. |
প্রয়োজনের নিরিখে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ |
বিচারক ও মামলার অনুপাতের উন্নয়ন |
দীর্ঘমেয়াদে |
আইন ও বিচার বিভাগ; জুডিশিয়াল কমিশন |
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; অর্থ বিভাগ |
|
৬. |
রেজিস্ট্রারের কার্যালয়কে শক্তিশালীকরণ |
রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের সেবা-মানের উন্নয়ন |
স্বল্পমেয়াদে |
আইন ও বিচার বিভাগ |
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; অর্থ বিভাগ |
|
৭. |
দেওয়ানি মামলার সময়সীমা নির্ধারণ |
দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তিতে সময়সীমা হ্রাসপ্রাপ্ত |
দীর্ঘমেয়াদে |
আইন ও বিচার বিভাগ |
|
|
৮. |
আদালত অবমাননার সংজ্ঞা নির্ধারণ |
আদালত অবমাননার সংজ্ঞা নির্ধারিত |
মধ্যমেয়াদে |
আইন ও বিচার বিভাগ |
|
|
৯. |
বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ |
বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি |
চলমান ও অব্যাহতভাবে |
আইন ও বিচার বিভাগ |
|
২.৪ নির্বাচন কমিশন
২.৪.১ প্রেক্ষাপট
(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক গঠিত এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োজিত প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য চারজন কমিশনার নিয়ে বর্তমানে নির্বাচন কমিশন সংবিধান-নির্দেশিত নির্বাচন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করার দায়িত্ব পালন করছেন। ‘অনুসন্ধান পদ্ধতি’ অনুসরণান্তে রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত প্যানেল হতে তিনি প্রধান ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করেছেন। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের ‘দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা’ নিশ্চিতকরণে ‘নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯’ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনের আওতায় নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন পরিচালনা করে। কমিশন সচিবালয়কে কমিশনের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে, কমিশনের খাতে এবং নিয়ন্ত্রণে আলাদা বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনায় কমিশনকে সক্ষম করার লক্ষ্যে একাধিক আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
(খ) নির্বাচন কমিশন নতুন নিয়োগবিধি প্রণয়নের মাধ্যমে সচিবালয় ও মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সমন্বিত করেছে। কাঠামোগত পরিবর্তন আনয়ন, অধিক সংখ্যক লোকবলের নিয়োগ ও সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এটি একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।
(গ) সংবিধানের ১১৮ ও ১১৯ অনুচ্ছেদের বলে নির্বাচন কমিশন নিয়োগের বিষয়ে অধিকতর স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
২.৪.২ চ্যালেঞ্জ
এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ:
- সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কমিশন গঠন;
- নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখা;
- বিদ্যমান নির্বাচন আইন ও বিধিমালার সুষ্ঠু প্রয়োগ;
- সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে কার্যকর অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা;
- নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করা;
- নির্বাচনী বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তি।
২.৪.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ
লক্ষ্য
অবাধ, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে সক্ষম সম্পূর্ণ স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নির্বাচন কমিশনকে কার্যকর রাখা।
স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ
- জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- নির্বাচন ব্যবস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- যথাযথ চাহিদা নিরূপণের ভিত্তিতে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং নির্বাচন কমিশন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে শক্তিশালী করা;
- উন্নততর প্রযুক্তির মাধ্যমে কমিশনের কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় উৎকর্ষ সাধন।
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ
- কমিশনারদের নিয়োগ এবং তাঁদের সুবিধা বিষয়ক আইন/ বিধিমালা/ নীতিমালার সংস্কার সাধন;
- নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো সরকার কর্তৃক অনুমোদন;
- উন্নততর নির্বাচনী সংস্কৃতি চর্চা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নির্বাচকমণ্ডলী ও প্রার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধি;
- নির্বাচনী বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার।
২.৪.৪ কর্মপরিকল্পনা
|
ক্রমিক |
কার্যক্রম |
কর্মসম্পাদন সূচক |
সময় |
দায়িত্ব |
সহায়তাকারী |
|---|---|---|---|---|---|
|
১. |
কমিশনারগণের নিয়োগ ও সুবিধাদি সম্পর্কে খসড়া আইন/ বিধিমালা/ নীতিমালা প্রণয়ন |
সংসদে বিবেচনার জন্য আইন-প্রস্তাব উপস্থাপিত
|
মধ্যমেয়াদে |
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
|
২. |
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ |
সরকারের বিবেচনার জন্য সাংগঠনিক কাঠামো উপস্থাপিত |
মধ্যমেয়াদে |
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় |
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
|
৩. |
সকল উপজেলা ও জেলা এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে সক্রিয় সার্ভার স্টেশন, ডাটাবেইজ ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার এবং ঢাকায় ইলেকশন রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ |
সকল উপজেলা ও জেলা এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে সক্রিয় সার্ভার স্টেশন, ডাটাবেইজ ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার এবং ঢাকায় ইলেকশন রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ |
স্বল্পমেয়াদে |
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন |
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
|
৪. |
নির্বাচন কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি |
মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ কমিশনের সকল কর্মকর্তা নির্বাচন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষিত |
চলমান |
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন |
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
|
৫. |
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও সুসজ্জিতকরণ |
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক; প্রশিক্ষণ সামগ্রীর লভ্যতা নিশ্চিত |
স্বল্পমেয়াদে |
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন |
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
|
৬. |
নির্বাচনী বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত আইন সংশোধন; নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের সক্ষমতা বৃদ্ধি |
নির্বাচনী বিরোধ দ্রুততর সময়ে নিষ্পন্ন |
মধ্যমেয়াদে |
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন |
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
|
৭. |
নির্বাচকমণ্ডলী, ভোটার ও ভোটপ্রার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা |
উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী করণীয় সম্পর্কে অবহিত |
স্বল্পমেয়াদে |
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন |
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
২.৫ অ্যাটর্নি জেনারেল
২.৫.১ প্রেক্ষাপট
(ক) অ্যাটর্নি জেনারেল একটি সাংবিধানিক পদ; এ পদের অধিকারী ব্যক্তি সরকারের মুখ্য আইন কর্মকর্তা। অ্যাটর্নি জেনারেল এবং তাঁর কার্যালয় রাষ্ট্রের স্বার্থ ও আইন সমুন্নত রাখার জন্য বিচার বিভাগকে সহায়তা দান করেন। অ্যাটর্নি জেনারেল বিভিন্ন মোকদ্দমায় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তাঁর কাছে প্রেরিত বিভিন্ন বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করেন। বর্তমানে ‘বাংলাদেশ আইন কর্মকর্তা আদেশ, ১৯৭২’ অনুসরণে রাষ্ট্রপতি অ্যাটর্নি জেনারেলকে নিয়োগদান করেন। তাঁর চাকরির মেয়াদ রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির ওপর নির্ভরশীল।
(খ) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও গণমানুষের সুবিচার-প্রাপ্তি এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে অ্যাটর্নি জেনারেল ও অন্যান্য আইন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাধীনভাবে এবং নিরপেক্ষতা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন অত্যন্ত জরুরি। অস্থায়ী নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্য আইনজীবীগণকে সুপ্রীম এ্যাডিশনাল, ডেপুটি ও এ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল হিসাবে এবং জেলা পর্যায়ে পাবলিক প্রসিকিউটর এবং সরকারি উকিল হিসাবে নিয়োগদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ লক্ষ্য পূরণে প্রয়োজনীয় আইন/বিধিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।
২.৫.২ চ্যালেঞ্জ
এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:
- অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং নিরপেক্ষ, দক্ষ ও ‘টেনিউরভিত্তিক’ পেশাদার আইন কর্মকর্তা নিয়োগ;
- অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের প্রতি উন্নততর বিশ্বাস ও আস্থার মনোভাব সৃষ্টি;
- দুর্নীতি ও ‘মানি লন্ডারিং’-এর মামলায় প্রতিনিধিত্বের জন্য পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন;
- দরিদ্র জনগণের আইনি সহায়তা নিশ্চিতকরণ।
২.৫.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ
লক্ষ্য
সংবিধান ও দেশের বিচার ব্যবস্থাকে সমুন্নত রাখার জন্য অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়কে একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা।
স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সুপারিশ
- আইন কর্মকর্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- আইন কর্মকর্তাগণের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ।
দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ
১. রাষ্ট্রস্বার্থ রক্ষার জন্য সুস্পষ্ট কার্যপরিধিসহ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ; অ্যাটর্নি জেনারেল ও অন্যান্য আইন কর্মকর্তার নিয়োগ ও সুবিধার বিষয়ে আইন/ বিধিমালা প্রণয়ন;
২. দেওয়ানি, রীট ও ফৌজদারি শাখার মত বিশেষায়িত ইউনিট স্থাপনপূর্বক অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় পুনর্গঠন;
৩. দরিদ্র জনগণের আইনি সহায়তা কার্যক্রম সম্প্রসারণ।
২.৫.৪ কর্মপরিকল্পনা
|
ক্রমিক |
কার্যক্রম |
কর্মসম্পাদন সূচক |
সময় |
দায়িত্ব |
সহায়তাকারী |
|
১. |
বিশেষায়িত ইউনিট (রীট, দেওয়ানি, ফৌজদারি) সৃষ্টির জন্য অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের পুনর্গঠন |
রীট. দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার জন্য পৃথক পৃথক ইউনিট গঠিত |
মধ্যমেয়াদে |
অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় |
আইন ও বিচার বিভাগ |
|
২. |
অ্যাটর্নি সার্ভিসেস আইন প্রণয়ন |
অ্যাটর্নি সার্ভিসেস আইন প্রণীত |
মধ্যমেয়াদে |
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ |
অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়; আইন ও বিচার বিভাগ |
|
৩. |
অস্থায়ী নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য (পাঁচ বছর) অ্যাটর্নি এ্যাডিশনাল, ডেপুটি ও এ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেলদের নিয়োগ প্রদান |
প্রস্তাবিত অ্যাটর্নি সার্ভিসেস আইন অনুসরণে নিয়োগদান |
মধ্যমেয়াদে |
আইন ও বিচার বিভাগ |
|
|
৪. |
আইন কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ |
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উন্নততর দক্ষতাসম্পন্ন আইন কর্মকর্তা |
স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে |
অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়; আইন ও বিচার বিভাগ |
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট |
|
৫. |
দরিদ্র জনগণের আইনি সহায়তা কার্যক্রমের পরিসর বৃদ্ধি |
অধিক সংখ্যক দরিদ্র মানুষের আইনি সহায়তা লাভ |
স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে |
অ্যাটর্নি জেনারেল; আইন ও বিচার বিভাগ |
অর্থ মন্ত্রণালয় |
২.৬ সরকারি কর্ম কমিশন
২.৬.১ প্রেক্ষাপট
(ক) সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সরকারি কর্ম কমিশন ‘প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিবৃন্দকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা’ করে, এবং ‘রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোন বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হইলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব সংক্রান্ত কোন বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইলে সেই সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ দান’ করে। রাষ্ট্রপতি কমিশনের সভাপতি এবং অন্যান্য সদস্যকে নিয়োগদান করেন, যাঁরা স্বাধীনভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন।
(খ) বর্তমান কমিশন পরীক্ষা পদ্ধতিতে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করেছে, ‘সিভিল সার্ভিস (সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়স, যোগ্যতা ও পরীক্ষা) বিধিমালা, ১৯৮২’-তে সংশোধন এনেছে; মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের সম্পাদক, সরকারি কর্মকর্তা, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং কর্পোরেট সংস্থার প্রধানদের সমন্বয়ে বিশেষজ্ঞ বোর্ড গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নকল্পে ‘কমিশন নিয়োগ বিধিমালা’ জারি করা হয়েছে। যোগ্য প্রার্থী বাছাই করার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত কিছু সংস্কারও সাধন করা হয়েছে।
(গ) নিয়োগের ক্ষেত্রে জটিলতা পরিহার এবং ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপক সমীক্ষার ভিত্তিতে বিদ্যমান কোটা পদ্ধতিকে যৌক্তিকীকরণের একটি প্রস্তাব বর্তমানে বিবেচনাধীন আছে। প্রজাতন্ত্রের কর্মে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদান ছাড়াও প্রজাতন্ত্রের কর্মে ‘এক শাখা থেকে অন্য শাখায় পদোন্নতি দান বা বদলিকরণের জন্য প্রার্থীর উপযোগিতা সম্পর্কিত অনুসরণীয় নীতিসমূহ’ সম্পর্কে তাঁকে পরামর্শদান কমিশনের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে কর্ম কমিশনের ভূমিকাকে আরো জোরদার করা প্রয়োজন।
২.৬.২ চ্যালেঞ্জ
এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:
- আর্থিক ও ব্যবস্থাপনাগত প্রশাসনসহ সরকারি কর্ম কমিশনের অধিকতর স্বাধীনতা অর্জন;
- সরকারি কর্ম কমিশনের অধিকতর বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন;
- অধিকতর স্বচ্ছ ও ত্রুটিহীন নিয়োগ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা;
- প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির মানদণ্ড নির্ধারণ;
- কমিশনের পরীক্ষাসমূহে আধুনিক পরীক্ষা কর্মকৌশলাদি অনুসরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কমিশন সচিবালয়ের উন্নততর সক্ষমতা অর্জন;
- কমিশনের অভ্যন্তরীণ জবাবদিহি পদ্ধতির উন্নতি সাধন;
- প্রতি বছর নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারে কর্মকর্তা নিয়োগ।
২.৬.৩ লক্ষ্য ও সুনির্দিষ্ট সুপারিশ
লক্ষ্য
উপযুক্ত সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়োগ সুপারিশ করার লক্ষ্যে সরকারি কর্ম কমিশনের একটি কার্যকর, আধুনিক ও পেশাদার প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ।
স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ
১. আধুনিক নিয়োগ প্রক্রিয়া বিষয়ে সরকারি কর্ম কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ
- মেধাভিত্তিতে অধিকতর নিয়োগ ও কোটা পদ্ধতি যৌক্তিকীকরণ;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি সংক্রান্ত মানদণ্ড নির্ধারণ ও তা বস্তবায়নের মাধ্যমে পদোন্নতি সুপারিশকরণ;
- সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যের নিয়োগের মানদণ্ড ও প্রক্রিয়া পুনর্বিবেচনা এবং অধিকতর স্বচ্ছ মনোনয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ;
- তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক মনোনয়ন পদ্ধতি প্রবর্তন (আবেদন প্রক্রিয়াকরণ, প্রাথমিক ও লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠান)।
- মৌখিক পরীক্ষায় স্বচ্ছতা ও বস্তুনিষ্ঠতা আনয়নের লক্ষ্যে ম্যানুয়েল প্রণয়ন;
- সাংবিধানিক অবস্থানের আলোকে কমিশনের ব্যবস্থাপনাগত ও আর্থিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও কমিশনের সচিবালয়কে শক্তিশালীকরণ;
- কমিশনের কর্মকাণ্ড একাধিক কমিশনের মধ্যে বিভাজনের মাধ্যমে প্রার্থী যাচাইকার্যে সুষ্ঠুতা ও দ্রুততা আনয়ন।
২.৬.৪ কর্মপরিকল্পনা
|
ক্রমিক |
কার্যক্রম |
কর্মসম্পাদন সূচক |
সময় |
দায়িত্ব |
সহায়তাকারী |
|
১. |
সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি ও সদস্যগণের মনোনয়ন নীতিমালা প্রণয়ন ও তদনুসারে কমিশনের সভাপতি ও অন্য সদস্যগণের মনোনয়ন প্রদান |
সভাপতি ও সদস্যদের মনোনয়ন নীতিমালা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত |
মধ্যমেয়াদে |
রাষ্ট্রপতির সচিবালয় |
সরকারি কর্ম কমিশন |
|
২. |
তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তন |
নয় থেকে বারো মাসের মধ্যে পাবলিক পরীক্ষার প্রক্রিয়া সম্পন্ন |
মধ্যমেয়াদে |
সরকারি কর্ম কমিশন |
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় |
|
৩. |
সুনির্দিষ্ট মান অনুযায়ী মৌখিক পরীক্ষা পরিচালনার জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন ও অনুসরণ |
মৌখিক পরীক্ষার নম্বর প্রদানে প্রমিতমান অর্জন |
মধ্যমেয়াদে |
সরকারি কর্ম কমিশন |
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় |
|
৪. |
কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পদোন্নতির মানদণ্ড নির্ধারণ ও এর বাস্তবায়ন |
কর্ম কমিশন কর্তৃক পদোন্নতির মানদণ্ড নির্ধারিত এবং বাস্তবায়িত |
মধ্যমেয়াদে |
সরকারি কর্ম কমিশন |
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় |
|
৫. |
কোটা পদ্ধতির যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে মেধা কোটা বৃদ্ধি |
মেধাভিত্তিতে অধিকতর সংখ্যক মনোনয়ন লাভ |
ধাপে ধাপে ও দীর্ঘমেয়াদে |
সরকারি কর্ম কমিশন
|
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় |
|
৬. |
সরকারি কর্ম কমিশনের আর্থিক ও ব্যবস্থাপনাগত স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে নীতি প্রণয়ন |
সরকারি কর্ম কমিশনের নির্ধারিত সুবিধাদি ও বাজেট লাভ এবং নিজস্ব কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সক্ষমতা অর্জন |
স্বল্পমেয়াদে |
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় |
সরকারি কর্ম কমিশন |
|
৭. |
সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক আধুনিক নিয়োগ পদ্ধতি বিষয়ে চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান |
চাহিদা নিরূপণ সম্পন্ন প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত |
স্বল্পমেয়াদে |
সরকারি কর্ম কমিশন |
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় |
|
৮. |
একাধিক কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা |
একাধিক কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠিত |
দীর্ঘমেয়াদে |
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় |
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও সরকারি কর্ম কমিশন |
২.৭ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
২.৭.১ প্রেক্ষাপট
(ক) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ (৫০% সরকারি শেয়ার বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানও এতে অন্তর্ভুক্ত) ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব নিরীক্ষা করেন এবং অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট রিপোর্ট প্রদান করেন। কর্মবৃত্তের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় রাষ্ট্রের ‘ওয়াচডগ’ হিসাবে কাজ করে।
(খ) মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক সম্পাদিত উল্লিখিত রিপোর্টসমূহে বিধিবিধানের অনুসরণ, আর্থিক নিরীক্ষা এবং কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে জনস্বার্থের সুরক্ষা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ উল্লেখ থাকে, যা পরবর্তী সময়ে সংসদে উপস্থাপন করা হয়। সরকারি হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এসব রিপোর্ট পর্যালোচনা করে নির্বাহী বিভাগকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সুপারিশ প্রদান করে। ‘ভ্যালু ফর মানি’ নিরীক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদানের জন্য একটি পৃথক ‘কৃতি নিরীক্ষা (performance audit) পরিদপ্তর’ গঠিত হয়েছে। ২০০৯ সাল নাগাদ এ পরিদপ্তর উনিশটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে যার মধ্যে চারটি প্রতিবেদন সরকারি হিসাব কমিটিতে ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে।
(গ) নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনার লক্ষ্যে সাচিবিক ব্যবস্থা তথা কমিটির সুপারিশ সঙ্কলন, সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠান/ মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ প্রেরণ, এবং কমিটির পরবর্তী সভায় আলোচনার জন্য উপস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষের অনুসৃত নিরীক্ষা-মান ও নিরীক্ষা পদ্ধতিকে যথাযথ মাত্রায় আধুনিকায়নও অত্যন্ত জরুরি।
২.৭.২ চ্যালেঞ্জ
এ ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:
- গ্রহণযোগ্য ও স্বাভাবিক সময়ের ব্যবধানে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের রিপোর্ট লভ্য হওয়া, যাতে তাঁর কার্যালয় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক দায়বদ্ধতা নিরূপণের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়;
- নিরীক্ষা-পর্যবেক্ষণাদি পরিপালনের জন্য মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান এবং প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি অনুসরণ;
- আধুনিক নিরীক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের (প্রাযুক্তিক ভিত্তিসহ) সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দক্ষ জনবল গঠন;
- নিরীক্ষা ও হিসাব কার্যক্রমের পৃথকীকরণ।
২.৭.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ
লক্ষ্য
সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে আর্থিক স্বচ্ছতার দাবিদার একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লাভ।
স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ
- শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নিরীক্ষাধীন সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ পরিপালন নিশ্চিতকরণ;
- যথাসময়ে নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য উন্মুক্তকরণ। এ-সম্পর্কিত আইন পরিবর্তন ও পরিমার্জন।
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ
- নিজ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে সংবিধানে প্রদত্ত স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক, প্রশাসনিক ও কারিগরি ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে এ কার্যালয়কে একটি সাংবিধানিক সংস্থা হিসাবে শক্তিশালীকরণ;
- সর্বোৎকৃষ্ট আন্তর্জাতিক মানের নিরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের জনবল নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি।
২.৭.৪ কর্মপরিকল্পনা
|
ক্রমিক |
কার্যক্রম |
কর্মসম্পাদন সূচক |
সময় |
দায়িত্ব |
সহায়তাকারী |
|---|---|---|---|---|---|
|
১. |
মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়কে আর্থিক, প্রশাসনিক ও কারিগরি দিকে হতে অধিকতর স্বশাসিত করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ |
জাতীয় সংসদ কর্তৃক নিরীক্ষা আইন পাশ |
মধ্যমেয়াদে |
মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ও অর্থ বিভাগ |
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় |
|
২. |
নিরীক্ষার পূঞ্জীভূত অনিষ্পন্ন কাজ সম্পাদনের জরুরি কর্মসূচি গ্রহণ |
সম্মত স্বাভাবিক বিলম্বিত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষা প্রতিবেদনসমূহ দাখিল |
স্বল্পমেয়াদে |
মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ও সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি |
সকল সরকারি দপ্তর |
|
৩. |
সর্বোৎকৃষ্ট আন্তর্জাতিক মানের নিরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের ‘টেকনিক্যাল অডিটিং’ ও ‘পারফরমেন্স অডিটিং’ ব্যবস্থা প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা |
‘টেকনিক্যাল অডিটিং’ ও ‘পারফরমেন্স অডিটিং’ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত |
মধ্যমেয়াদে |
মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় |
সকল সরকারি দপ্তর |
|
৪. |
দণ্ডমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নিরীক্ষাধীন সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ পরিপালন নিশ্চিত করার কার্যব্যবস্থা গ্রহণ |
সকল নিরীক্ষাধীন সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণের জবাবদান এবং তা না করা হলে সরকার কর্তৃক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ |
স্বল্পমেয়াদে |
মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ও অর্থ বিভাগ |
সকল সরকারি দপ্তর |
|
৫. |
‘ভ্যালু ফর মানি’ নিশ্চিতকরণ জন্য ‘সোসাল পারফরমেন্স অডিট’-এর দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন |
কর্মপরিকল্পনা প্রণীত |
স্বল্পমেয়াদে |
মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় |
অর্থ বিভাগ |
|
৬. |
নিরীক্ষা ও হিসাব কার্যক্রমের পর্যায়ক্রমিক পৃথকীকরণ |
নিরীক্ষা ও হিসাব পৃথক কার্যক্রম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত |
মধ্যমেয়াদে |
মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় |
অর্থ বিভাগ |
২.৮ ন্যায়পাল
২.৮.১ প্রেক্ষাপট
(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদের আওতায় ন্যায়পাল আইন পাশ হয়েছে। ন্যায়পাল নিয়োগ এবং ন্যায়পালের দপ্তর প্রতিষ্ঠা এখনও অসম্পন্ন রয়েছে। ন্যায়পালের দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হলে তা একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংক্ষুব্ধ নাগরিকদের অভিযোগ গ্রহণ করবে, সে-সম্পর্কে অনুসন্ধান পরিচালনা করবে এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
(খ) ন্যায়পালের দপ্তর যাতে স্বাধীন সত্তা নিয়ে কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে তার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটিকে আর্থিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতে হবে। ন্যায়পালের ক্ষমতা ও অধিক্ষেত্রও সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে।
২.৮.২ চ্যালেঞ্জ
এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:
- ন্যায়পাল নিয়োগ ও ন্যায়পালের দপ্তর প্রতিষ্ঠা;
- অন্যান্য সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের (যেমন, দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন) সঙ্গে দায়িত্ব ও কৃত্যের দ্বৈততা পরিহার।
২.৮.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ
লক্ষ্য
কার্যকর ন্যায়পাল দপ্তর প্রতিষ্ঠা ।
স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ
- ন্যায়পাল নিয়োগ, তাঁর দপ্তর প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দ করা;
- ন্যায়পালের দপ্তরের জন্য কার্যপরিচালনা নীতিমালা, কর্মপ্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রণয়ন।
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ
- সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, কর্মপরিসর ও আর্থিক স্বায়ত্তশাসনের নিরিখে ‘ন্যায়পাল আইন, ১৯৮০’ পর্যালোচনা করা এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দায়িত্ব ও কৃত্যের দ্বৈততা পরিহারের ব্যবস্থা গ্রহণ।
২.৮.৩ কর্মপরিকল্পনা
|
ক্রমিক |
কার্যক্রম |
কর্মসম্পাদন সূচক |
সময় |
দায়িত্ব |
সহায়তাকারী |
|
১. |
ন্যায়পাল, তাঁর দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের নিয়োগ |
ন্যায়পাল, কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিয়োজিত |
স্বল্পমেয়াদে |
সংসদ |
জাতীয় সংসদ সচিবালয় |
|
২. |
ন্যায়পালের কার্যালয়ের ভৌত সুবিধাদি এবং ঢাকা ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও সামগ্রী সরবরাহ |
প্রয়োজনীয় ভৌত সুবিধা ও সরঞ্জামসহ ন্যায়পালের দপ্তর ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত |
স্বল্পমেয়াদে |
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ |
জাতীয় সংসদ সচিবালয়;
|
|
৩. |
ন্যায়পালের দপ্তরের কর্মপরিচালনার বিধিবিধান ও কার্যপদ্ধতি প্রণয়ন |
বিধিবিধান ও কার্যপদ্ধতি প্রণীত |
মধ্যমেয়াদে |
জাতীয় সংসদ সচিবালয়;
|
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ |
|
৪. |
ন্যায়পালের দপ্তরের কার্যাবলি পর্যালোচনা ও পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন |
সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন প্রণীত |
মধ্য মেয়াদে |
ন্যায়পাল |
জাতীয় সংসদ সচিবালয়; লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ |
২.৯ দুর্নীতি দমন কমিশন
২.৯.১ প্রেক্ষাপট
(ক) দুর্নীতির বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে লড়াই এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সরকার নতুন আইনের আওতায় দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কার্যক্রম ও কাঠামো সংস্কারের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। নতুন কমিশন পুরাতন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে যাত্রা শুরু করে ইতোমধ্যে নতুন কাঠামো ও কর্মপরিধি প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রতিষ্ঠানটি জনপ্রশাসন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সিভিল সোসাইটির প্রতিষ্ঠান ও এগুলিতে নিযুক্ত ব্যক্তিবৃন্দের দুর্নীতিমূলক কার্যাদি নিয়ে অনুসন্ধান চালায়, তদন্ত পরিচালনা করে এবং সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে অভিযোগ দায়ের ও মামলা পরিচালনার মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
(খ) সরকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগ এবং কাঠামো অনুযায়ী বর্ধিত লোকবল নিয়োজিত করেছে। কমিশনকে অধিকতর দক্ষ ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তথ্যপ্রযুক্তি, অনুসন্ধান ও তদন্তকার্য, ‘হোয়াইট কলার’ অপরাধ, ‘মানি লন্ডারিং’ অভিযুক্তের অধিকার, ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে এবং অভ্যন্তরীণ দায়বদ্ধতা ছাড়াও কমিশন আন্তর্জাতিক পর্যায়ের একটি দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। বড় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অর্থপাচার রোধকল্পে বাংলাদেশ ‘মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২’ পাশ করেছে এবং তার বাস্তবায়নে দুর্নীতি দমন কমিশন কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।
(গ) দুর্নীতি দমন কমিশনকে আর্থিক, প্রশাসনিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অর্থ পাচারসহ অন্যান্য দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের ব্যাপক অনুসন্ধান, তদন্ত এবং মামলা পরিচালনা করতে হয় বিধায় এর সক্ষমতা ও দক্ষতা প্রভূতভাবে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং এর স্বাধীনতা নিশ্চিত করা জরুরি। দুর্নীতি সম্পর্কিত তদন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিশনের নিরপেক্ষতা সমুন্নত রেখে তার দায়বদ্ধতাও নিশ্চিত করা প্রয়োজন; সেই লক্ষ্যে আইনও সংস্কার করা আবশ্যক।
২.৯.২ চ্যালেঞ্জ
এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:
- স্বাধীনভাবে এবং নিরপেক্ষতার সঙ্গে কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক ও আইনি ক্ষমতা লাভ;
- দুর্নীতি দমন কমিশনের নিরপেক্ষতা সমুন্নত রাখা এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ;
- মানসম্পন্ন সেবাদান নিশ্চিত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও জনবল-সংশ্লিষ্ট সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- কমিশন কর্তৃক পর্যাপ্ত সম্পদ লাভ;
- তদন্তকার্য পরিচালনা ও অভিযোগ দাখিলের ক্ষেত্রে কমিশনের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- দুর্নীতি দমনে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের দৃঢ়ভাবে শুদ্ধাচার অনুসরণ, তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ;
- দুর্নীতিবিরোধী অবস্থানে নাগরিক ও আইন-প্রণেতাদের দৃঢ় সমর্থন প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি।
২.৯.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ
লক্ষ্য
দুর্নীতি দমনে কার্যকর একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিষ্ঠালাভ।
স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ
- কমিশনের দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- দুর্নীতি সম্পর্কে তথ্য-প্রদানকারীদের সুরক্ষায় সহায়তা প্রদান;
- দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠনে নাগরিকদের সম্পৃক্ত করার জন্য যোগাযোগ কর্মকৌশল প্রবর্তন;
- নিয়মিতভাবে কমিশনের সদস্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব প্রদান এবং কমিশনের ওয়েবসাইটে তা প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- দুর্নীতির তদন্ত পরিচালনায় কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ;
- দুর্নীতি দমন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ।
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ
- সর্বোৎকৃষ্ট দুর্নীতি প্রতিরোধ পরাকৌশলের অনুকরণ ও অনুশীলন;
- দুর্নীতি প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নাগরিক গোষ্ঠী ও গণমাধ্যমের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ অব্যাহত রাখা।
২.৯.৪ কর্মপরিকল্পনা
|
ক্রমিক |
কার্যক্রম |
কর্মসম্পাদন সূচক |
সময় |
দায়িত্ব |
সহায়তাকারী |
|---|---|---|---|---|---|
|
১. |
আইনি কাঠামো সংস্কারের মাধ্যমে কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং তদন্ত পরিচালনায় পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান |
বিদ্যমান আইন সংশোধিত |
স্বল্পমেয়াদে |
দুর্নীতি দমন কমিশন |
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
|
২. |
কমিশনের কার্যক্রমের অধিকতর নিরপেক্ষতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ |
বিদ্যমান আইন সংশোধিত |
মধ্যমেয়াদে |
দুর্নীতি দমন কমিশন |
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
|
৩. |
কমিশনের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ |
প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণীত ও তদনুসারে কার্যক্রম বাস্তবায়িত |
চলমান |
দুর্নীতি দমন কমিশন |
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
|
৪. |
বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন |
দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক চাহিবামাত্র তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ লাভ |
স্বল্পমেয়াদে |
দুর্নীতি দমন কমিশন |
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ |
|
৫. |
প্রমাণিত উৎকৃষ্ট অনুশীলন (best practices) অনুকরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধন |
উৎকৃষ্ট অনুশীলন-পদ্ধতির উত্তরোত্তর বাস্তবায়ন |
মধ্যমেয়াদে |
দুর্নীতি দমন কমিশন |
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
|
৬. |
সরকারি প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ |
কার্যকর দুর্নীতি-বিরোধী অভিযান বাস্তবায়িত |
স্বল্পমেয়াদে এবং অব্যাহতভাবে |
দুর্নীতি দমন কমিশন |
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
|
৭. |
দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার ইউনিট ও নৈতিকতা কমিটি গঠন ও শক্তিশালীকরণে সহায়তা প্রদান |
‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ অনুযায়ী শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ইউনিটসমূহ গঠিত ও কার্যকর |
স্বল্পমেয়াদে |
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
দুর্নীতি দমন কমিশন |
|
৮. |
দুর্নীতি প্রতিরোধে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য মনিটরিং সেল প্রতিষ্ঠা |
মনিটরিং সেল প্রতিষ্ঠিত |
স্বল্পমেয়াদে |
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
দুর্নীতি দমন কমিশন |
|
৯. |
জনপ্রতিনিধিসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে দুর্নীতি-বিরোধী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা |
নেতৃবৃন্দের দুর্নীতি-বিরোধী প্রচারণা ও কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ |
স্বল্পমেয়াদে |
দুর্নীতি দমন কমিশন |
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
|
১০. |
অর্থসম্পদ পাচার রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ |
‘মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন’ অব্যাহতভাবে বাস্তবায়িত |
স্বল্পমেয়াদে ও অব্যাহতভাবে |
দুর্নীতি দমন কমিশন |
বাংলাদেশ ব্যাংক |
২.১০ স্থানীয় সরকার
২.১০.১ প্রেক্ষাপট
(ক) সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদবলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিষ্ঠা এবং তাদের কার্যাবলি পরিচালিত হয়। সংবিধানে বিধৃত আছে যে, ‘আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে’ এবং এই প্রতিষ্ঠানসমূহ ‘(ক) প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্য; (খ) জনশৃঙ্খলা রক্ষা’; এবং (গ) ‘জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন’ করতে পারবে। এই ভিত্তিতেই স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার বিকশিত হয়েছে এবং বর্তমানে ইউনিয়ন স্তরে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা স্তরে উপজেলা পরিষদ, জেলা স্তরে জেলা পরিষদ এবং রাজধানী, বিভাগ ও বড় জেলা শহরে সিটি কর্পোরেশন এবং ছোট শহরে পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
(খ) বর্তমান সরকারের আমলে পরিচালিত নির্বাচনসমূহে ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদসমূহ এবং পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহে জনপ্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও স্থানীয়ভাবে বাস্তবায়নযোগ্য উন্নয়ন প্রকল্প ও পরিকল্পনাসমূহে সরকার সম্পদের পরিমাণও বৃদ্ধি করেছে।
(গ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের সম্পদ বরাদ্দের ওপর নির্ভরশীল। এ বরাদ্দ এবং সেইসঙ্গে তাদের সম্পদ আহরণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতা উন্নয়নও জরুরি। সর্বোপরি নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং এসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি কর্মকাণ্ড, এনজিওদের কার্যক্রম, স্থানীয় উদ্যোগ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধারণ নাগরিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। স্থানীয় সরকারসমূহে নির্বাচিত প্রতিনিধি, আইনপ্রণেতা ও নির্বাহী বিভাগের দায়িত্বপালনকারীদের ভূমিকা ও দায়িত্বও স্পষ্ট করা প্রয়োজন।
(ঘ) ‘আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে’ মর্মে সংবিধানে যে প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছিল তা কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ার থেকে স্থানীয় সরকারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণ (devolution) নির্দেশ করে। স্থানীয় সরকারে, বিশেষত গ্রামীণ স্থানীয় সরকারে কার্যকরভাবে এ ধরনের বিকেন্দ্রীকরণ এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অধিকন্তু, স্থানীয় সরকারের স্তরও একাধিক। কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারের ‘সংরক্ষিত’ ও ‘হস্তান্তরিত’ বিষয়াদি চিহ্নিত করাও দুষ্কর। সুতরাং স্থানীয় সরকারের মূল কেন্দ্র চিহ্নিত করাও প্রয়োজন।
২.১০.২. চ্যালেঞ্জ
এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:
- স্থানীয় পর্যায়ে সেবাসমূহের মান উন্নয়ন ও সমন্বয় সাধন;
- স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়বদ্ধতা-পদ্ধতির উন্নয়ন;
- স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা- কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- সামাজিক-অর্থনৈতিক-ভৌগোলিক বাস্তবতার আলোকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে সম্পদ বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ;
- স্থানীয় সরকারের কেন্দ্রবিন্দু স্থিরীকরণ;
- দায়িত্ব ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ;
- স্থানীয় রাজস্ব সংগ্রহ ও তার ভিত্তি বৃদ্ধি করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ।
২.১০.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ
লক্ষ্য
স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ, স্বনির্ভর, গণকেন্দ্রিক এবং ত্বরিত সাড়া দানে সক্ষম স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা।
স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ
- স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ;
- উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্যগণের এখতিয়ার সুনির্দিষ্টকরণ;
- জেলা পরিষদের কর্মপরিধি নির্দিষ্ট করা এবং জেলা-স্তরে কর্মরত অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে সম্পর্ক স্পষ্টীকরণ।
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ
- সরকারি সম্পদে জনগণের উন্নততর ও ন্যায্যতর অধিকার প্রতিষ্ঠা;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন;
- স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সৃজনশীল এবং বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ।
- স্থানীয় সরকারে নিয়োজিত জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ‘স্থানীয় সরকার সার্ভিস’ প্রতিষ্ঠা।
২.১০.৪ কর্ম-পরিকল্পনা
|
ক্রমিক |
কার্যক্রম |
কর্মসম্পাদন সূচক |
সময় |
দায়িত্ব |
সহায়তাকারী |
|
১. |
সামাজিক-অর্থনৈতিক-ভৌগোলিক বাস্তবতার আলোকে (জনসংখ্যা, আয়তন, অনগ্রসরতা) স্থানীয় সরকারসমূহে সম্পদ বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ |
বাৎসরিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বরাদ্দ |
স্বল্পমেয়াদে |
স্থানীয় সরকার বিভাগ |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ |
|
২. |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের ভিত্তির পরিসর বৃদ্ধিকরণ |
নতুন ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কর সংগ্রহের সুযোগদান; ‘বিক্রয় কর’, ‘মূল্য সংযোজন কর’ আহরণ করার আইনি ভিত্তি প্রদান |
মধ্যমেয়াদে |
স্থানীয় সরকার বিভাগ |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ |
|
৩. |
স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা, কর্মচারীদের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের জন্য নাগরিক উদ্যোগ গ্রহণ |
সংগঠিত নাগরিকগোষ্ঠী কর্তৃক রিপোর্ট কার্ড দাখিল এবং স্থানীয় সরকারের সংস্থাসমূহ থেকে তথ্য লাভ |
মধ্যমেয়াদে |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ |
সুশীল সমাজ; পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান |
|
৪. |
স্থানীয় সরকারে (বিশেষত উপজেলা ও জেলা পরিষদ) সংসদ সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তাগণের ভূমিকা ও এখতিয়ার সুনির্দিষ্টকরণ |
গাইডলাইন প্রণীত |
স্বল্পমেয়াদে |
স্থানীয় সরকার বিভাগ |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ |
|
৫. |
জেলা পরিষদের কর্মপরিধি নির্ধারণ এবং জেলাকে স্থানীয় সরকারের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে চিহ্নিতকরণ |
কর্মপরিধি নির্ধারিত ও স্পষ্টীকৃত |
মধ্যমেয়াদে |
স্থানীয় সরকার বিভাগ |
|
|
৬. |
স্থানীয় সরকার সার্ভিস প্রবর্তন |
স্থানীয় সরকার সার্ভিস বিধি প্রণয়ন ও তদনুসারে লোকবল নিয়োগ। |
দীর্ঘমেয়াদে |
স্থানীয় সরকার বিভাগ |
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় |
|
৭. |
স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ |
প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের প্রতিবেদন |
চলমান |
স্থানীয় সরকার বিভাগ |
সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ |
অধ্যায় ৩
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল — অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান
৩.১ রাজনৈতিক দল
৩.১.১ প্রেক্ষাপট
(ক) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বহু রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ও ক্রিয়াশীলতা অপরিহার্য। রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যবর্তী অবস্থানে থেকে এবং দল কর্তৃক মনোনীত ও জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে রাজনীতিবিদগণ রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের কৃত্য পরিচালনা করেন। তাঁরা আইনসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়ে আইন প্রণয়ন করেন, সরকার গঠন করে রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ পরিচালনা করেন। বাংলাদেশে বর্তমানে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৩৬টি।
(খ) বাংলাদেশে স্বাধীনতা অর্জন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলসমূহই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে সামরিক শাসন প্রত্যক্ষ করেছে। তবে, দেশে অধিকাংশ সময়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলসমূহ মূল শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। সার্বিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক দলসমূহের কর্মকাণ্ডে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠাও অত্যন্ত জরুরি – তাদের আর্থিক স্বচ্ছতা বজায় রাখা, তহবিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অডিট সম্পন্ন করা এবং সাংগঠনিক ক্রিয়াকাণ্ডে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতির প্রতিফলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
৩.১.২ চ্যালেঞ্জ
এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:
- রাজনৈতিক দলসমূহে অধিকতর গণতন্ত্র-চর্চা;
- দলের তহবিল ব্যবস্থাপনায় অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন;
- নাগরিকদের প্রয়োজন সম্পর্কে অধিকতর সচেতনতা প্রদর্শন;
- সাংঘর্ষিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিহার।
৩.১.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ
লক্ষ্য
নির্বাচকমণ্ডলীর স্বার্থের প্রতিভূ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ।
স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ
১. গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও প্রবর্তন;
দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ
- সুস্পষ্ট নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন ও নির্বাচনের পর তার যথাযথ বাস্তবায়ন;
- রাজনৈতিক দলের তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা;
- রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক একটি সম্মত আচরণবিধি প্রণয়ন ও অনুসরণ।
৩.১.৪ কর্মপরিকল্পনা
|
ক্রমিক |
কার্যক্রম |
কর্মসম্পাদন সূচক |
সময় |
দায়িত্ব |
সহায়তাকারী/ তত্ত্বাবধানকারী |
|
১. |
গণপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুসরণে দলসমূহের গঠনতন্ত্র বাস্তবায়ন |
সকল দলের (কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে) কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠান |
স্বল্পমেয়াদে এবং অব্যাহতভাবে |
রাজনৈতিক দলসমূহ |
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন |
|
২. |
রাজনৈতিক দলের আচরণ সম্পর্কে সম্মত বিধি প্রণয়ন ও অনুসরণ |
একটি সম্মত আচরণবিধি প্রণীত |
মধ্যমেয়াদে |
রাজনৈতিক দলসমূহ |
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন |
|
৩. |
প্রার্থী মনোনয়ন ও দলীয় তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন |
প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে সভা অনুষ্ঠান; দলীয় নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে কাউন্সিল অনুষ্ঠান; দলীয় তহবিলের আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব লভ্য |
চলমান |
রাজনৈতিক দলসমূহ |
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন |
|
৪. |
ট্রেড ইউনিয়ন, সুশীল সমাজ ও পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের পরামর্শ উৎসাহিতকরণ |
বৈঠক অনুষ্ঠিত ও যৌথ কার্যক্রম গৃহীত |
চলমান |
রাজনৈতিক দলসমূহ |
ট্রেড ইউনিয়নসমূহ, সুশীল সমাজ |
৩.২ বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান
৩.২.১ প্রেক্ষাপট
বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি খাত ক্রমবর্ধমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং স্বাধীনতার পর থেকে এর ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এখন ব্যবসায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করছে, সম্পদ সৃষ্টি ও তাতে মূল্যসংযোজনে নিয়োজিত রয়েছে এবং জনগণের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করছে। জিডিপিতে বেসরকারি খাতের অবদান ক্রমবর্ধমান। বিপুল আয়তনের এই সেক্টরের শুদ্ধাচার যেমন উন্নয়নের জন্য জরুরি তেমনই জনকল্যাণ ও জনসেবা নিশ্চিত করার জন্যও তা আবশ্যকীয়। বেসরকারি খাতে কর্পোরেট সংস্কৃতির প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। ঋণখেলাপি সংস্কৃতির অবসানও জরুরি। ভোক্তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ‘ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯’-এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন প্রয়োজন। ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের ষড়যন্ত্রমূলক আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাংকিং, ফাইন্যান্সিয়াল ও নন-ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল খাতের কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠাও প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। দুর্নীতির মাধ্যমে লব্ধ অর্থের অন্যতম উৎস ও আধার যেহেতু ব্যাংকিং খাতের প্রতিষ্ঠান, সেহেতু তাদের সুষ্ঠু ও নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রয়োজন। সম্প্রতি ‘মাল্টিলেভেলিং মার্কেটিং’ ব্যবসা প্রসার লাভ করেছে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে তা প্রভূত দুর্নীতির জন্ম দিচ্ছে। এ ধরনের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আইনের অপর্যাপ্ততা লক্ষ্য করা গেছে; সুতরাং এজন্য কার্যকর আইন প্রণয়নও জরুরি হয়ে পড়েছে।
৩.২.২ চ্যালেঞ্জ
এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:
- ব্যাংক-ঋণখেলাপি সমস্যার সমাধান;
- উন্নততর কর্পোরেট ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন;
- কর্মচারিদের ন্যায্য ও কর্ম সম্পাদনভিত্তিক মজুরি ও বেতন প্রদান;
- ভোক্তা অধিকার ও দেউলিয়া আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ;
- মাল্টিলেভেল মার্কেটিং ব্যবসায়ে নিয়মনিষ্ঠা আনয়ন;
- ব্যবসায় প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়ন করে যোগসাজশমূলক আচরণ প্রতিরোধ;
- চেম্বার ও সমিতিসমূহের মধ্যে স্বনিয়ন্ত্রণ, স্বচ্ছতা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা।
৩.২.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ
লক্ষ্য
জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নে দায়বদ্ধ ও গণমুখী খাত হিসাবে স্বচ্ছ বেসরকারি শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতের প্রতিষ্ঠা।
স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ:
- বেসরকারি খাতের নিয়ন্ত্রণকারী আইন, যেমন, ‘দেউলিয়া আইন’, ‘ভোক্তা সুরক্ষা আইন’-এর কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ;
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ:
- বেসরকারি খাতের উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত সরকারি প্রতিষ্ঠান, যেমন, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ‘ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি সেন্টার’-প্রভৃতির কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- মূল্য নির্ধারণে একাধিপত্য প্রতিরোধ, পরিবেশ সংরক্ষণ, শ্রম আইন অনুসরণ এবং ন্যূনতম ও ন্যায্য মজুরি প্রদানের বিষয়ে চেম্বার ও সমিতিসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি জোরদারকরণ;
- শুদ্ধাচারের অগ্রদূত হিসাবে চিহ্নিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুরস্কৃত করার মাধ্যমে উৎকৃষ্ট অনুশীলনকে উৎসাহিত করা;
- ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাযথ আয়কর প্রদানে উৎসাহিত ও বাধ্য করা;
- জাতীয় বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা পরিষদ (National Commercial Competitive Council) গঠন;
- অনৈতিক উপায়ে ব্যবসা সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইনি ও প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা;
- ‘মাল্টিলেভেল মার্কেটিং’ ব্যবসার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা।
৩.২.৪ কর্মপরিকল্পনা
|
ক্রমিক |
কার্যক্রম |
কর্মসম্পাদন সূচক |
সময় |
দায়িত্ব |
সহায়তাকারী |
|---|---|---|---|---|---|
|
১. |
ব্যবসায় স্বনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ |
চেম্বার সমিতিসমূহ কর্তৃক বিধি প্রতিপালিত এবং লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গৃহীত |
চলমান |
চেম্বার ও সমিতিসমূহ |
বাণিজ্যিক কোম্পানিসমূহ |
|
২. |
ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে দেউলিয়া আইনের কার্যকর প্রয়োগ |
দ্রুত মামলা রুজু এবং রায় প্রদান |
চলমান |
বাংলাদেশ ব্যাংক |
চেম্বার ও সমিতিসমূহ; ব্যাংক ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান |
|
৩ |
ব্যবসায় প্রতিযোগিতা আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন |
জাতীয় বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর |
চলমান |
বাণিজ্য মন্ত্রণালয় |
ব্যবসায়ী সমিতিসমূহ |
|
৪. |
কর্পোরেট পরিচালন বিধি লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ |
কর্পোরেট সংস্থার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গৃহীত |
চলমান |
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন |
অর্থ মন্ত্রণালয় |
|
৫ |
ন্যায্যতা ও কৃতিভিত্তিক বেতন, মজুরি ও সুবিধাদি প্রদানের বিষয়ে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা |
শিল্পক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতমূলক ঘটনার হ্রাস |
স্বল্পমেয়াদে এবং অব্যাহতভাবে |
বাণিজ্য মন্ত্রণালয় |
শিল্প মন্ত্রণালয়; শ্রম মন্ত্রণালয়; চেম্বার ও সমিতিসমূহ |
|
৬. |
যথাযথ ও নিয়মিত কর পরিশোধে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিতকরণ এবং শ্রেষ্ঠ অনুশীলনকারীদের পুরষ্কার প্রদান |
ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত করের পরিমাণ বৃদ্ধি |
চলমান ও অব্যাহতভাবে |
বাণিজ্য মন্ত্রণালয় |
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড; ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহ, |
|
৭. |
ভোক্তা অধিকার আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন |
ভোক্তাগণের সন্তুষ্টি |
চলমান এবং অব্যাহতভাবে |
বাণিজ্য মন্ত্রণালয় |
শিল্প মন্ত্রণালয়; চেম্বার ও সমিতিসমূহ |
|
৯. |
মাল্টিলেভেল মার্কেটিং ব্যবসার ক্ষেত্রে আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা |
নতুন আইন প্রণীত ও অনুসৃত |
স্বল্পমেয়াদে |
বাণিজ্য মন্ত্রণালয় |
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় |
|
১০. |
‘মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি’র পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা |
মাইক্রোক্রেডিট কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত |
চলমান ও অব্যাহতভাবে |
বাংলাদেশ ব্যাংক |
এনজিও ব্যুরো |
|
১১. |
‘ইনসিওরেন্স ডেভেলপম্যান্ট অ্যান্ড রেগুলেটরি অথরিটি’র (আইডিআরএ) কার্যক্রম জোরদার করা |
বীমা কার্যক্রমের পরিসর ও স্বচ্ছতায় উন্নয়ন সাধিত |
চলমান ও অব্যাহতভাবে |
বাণিজ্য মন্ত্রণালয় |
অর্থ মন্ত্রণালয় |
৩.৩ এনজিও ও সুশীল সমাজ
৩.৩.১ প্রেক্ষাপট
(ক) "পরিবার, রাষ্ট্র এবং শিল্প-বাণিজ্যের বাইরে বিভিন্ন পেশার মানুষ যেখানে তাদের স্বার্থ সুরক্ষা ও কল্যাণ প্রচেষ্টায় সংগঠিত হয়, তাকে সুশীল সমাজ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়"। সুশীল সমাজ বাংলাদেশে একটি সক্রিয় খাত এবং এর অন্যতম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ হচ্ছে বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান(এনজিও)সমূহ। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ঘোষিত লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন এনজিও কাজ করে চলেছে এবং ইতোমধ্যে বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী এনজিও সেক্টর প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। এছাড়া, সরকার ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের বাইরে অনেক শিক্ষক, গবেষক, পেশাজীবী, উন্নয়নকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবী স্বতঃপ্রণোদিতভাবে উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করছেন; সেবামূলক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন ইস্যুতে জনমত গঠন এবং গণমানুষের সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করে চলেছেন। সামগ্রিকভাবে তারা সুশীল সমাজ হিসাবে পরিচিত।
(খ) যদিও স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে সুশীল সমাজ ও এনজিওসমূহ প্রাথমিকভাবে তাদের নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও পদ্ধতির নিকট দায়বদ্ধ, কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা রাষ্ট্রের আইনকানুন ও সামাজিক প্রথার কাছে দায়বদ্ধ। রাষ্ট্র ক্ষেত্রবিশেষে তাদের কার্যক্রমে আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করে, এবং তারাও রাষ্ট্রের কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান করে। কিন্তু তাদের মূল কাজ হল রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসায়িক কর্মবৃত্তের বাইরে থেকে উন্নয়নে সহায়তা প্রদান এবং রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রমের দায়বদ্ধতা দৃশ্যমান করে গণমানুষের স্বাধীনতার পরিসর বৃদ্ধি ও উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ। গণতন্ত্রের বিকাশে তারাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
(গ) সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ ও এনজিওসমূহের কার্যক্রমে দলনিরপেক্ষতা বজায় রাখা, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা পরিহার করা এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে আর্থিক স্বচ্ছতা অনুশীলন করা তাদের কার্যক্রমে শুদ্ধাচারের মাপকাঠি বলে বিবেচিত। এসব ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন অত্যন্ত জরুরি। এনজিও-র কার্যক্রমকে স্বচ্ছতর করা এবং তাদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত আইনি কাঠামো সৃষ্টি, স্বচ্ছ নিয়োগ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা, সরকারের সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসনও গুরুত্বপূর্ণ।
৩.৩.২ চ্যালেঞ্জ
এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:
- প্রযোজ্য আইনি কাঠামের মধ্যে এনজিওসমূহের কার্যক্রম পরিচালনা;
- সুশীল সমাজের দলনিরপেক্ষ ভূমিকা পালন;
- সরকার, সুবিধাভোগী ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী এনজিওদের দায়বদ্ধতার উন্নয়ন;
- এনজিও-র কার্যকর পরিবীক্ষণ, আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং যাবতীয় কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;
- এনজিওর কার্যক্রমে আমলাতান্ত্রিকতা হ্রাস ও তার প্রসার উৎসাহিতকরণ।
৩.৩.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ
লক্ষ্য
দায়বদ্ধ ও গণমানুষের উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠা।
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ:
- আইনপ্রণেতা, নীতিনির্ধারক ও গণমাধ্যমের সঙ্গে অধিকতর মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ সৃষ্টি;
- এনজিওদের নিবন্ধনের জন্য একক নিবন্ধন-সংস্থা প্রতিষ্ঠা;
- এনজিও সংক্রান্ত আইন ও বিধিসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন;
- এনজিওসমূহের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ;
- এনজিওদের কর্মকাণ্ডে অধিকতর দায়বদ্ধতার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নাগরিকদের মতামত প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি;
- প্রত্যন্ত এলাকায় অতিদরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এনজিওদের কার্যক্রমের সম্প্রসারণ;
- এনজিওদের গভর্নেন্স পদ্ধতিতে সংস্কার সাধন ও তাদের কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন।
৩.৩.৪ কর্মপরিকল্পনা
|
ক্রমিক |
কার্যক্রম |
কর্মসম্পাদন সূচক |
সময় |
দায়িত্ব |
সহায়তাকারী |
|
১. |
সরকারি নীতিনির্ধারণমূলক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সুশীল সমাজের সঙ্গে অধিকতর মিথস্ক্রিয়ার (interaction) সুযোগ সৃষ্টি |
আয়োজিত সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়ামে সুশীল সমাজের সদস্যবৃন্দ, এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ; সুশীল সমাজের পরামর্শ দান, তাদের গবেষণামূলক কাজ ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার বিকাশ |
চলমান ও দীর্ঘমেয়াদে |
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো |
তত্ত্বাবধানে: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় |
|
২. |
এনজিওদের কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন
|
এনজিও ও স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট দাখিলকৃত রিপোর্ট কার্ড; বাৎসরিক বাজেট জনসমক্ষে প্রকাশ; ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে কার্যক্রম উপস্থাপন |
স্বল্পমেয়াদে |
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো |
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় |
|
৩. |
এনজিওদের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়ন |
এনজিওদের সেবা-প্রদানকারী, সেবা-গ্রহীতাদের সংগঠনের পদ্ধতি, উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুষ্ঠু তথ্য লাভ ও অনুসরণ |
দীর্ঘমেয়াদে |
এনজিওসমূহ; এনজিও বিষয়ক ব্যুরো |
তত্ত্বাবধানে: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় |
|
৪. |
এনজিওসমূহের প্রমিত হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তন |
প্রমিত হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তিত |
মধ্যমেয়াদে |
এনজিওসমূহ; এনজিও বিষয়ক ব্যুরো |
তত্ত্বাবধানে: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় |
|
৫. |
এনজিও-র নিয়োগে স্বচ্ছতা বিধানে প্রয়োজনীয় আইন/বিধি/ নীতিমালা প্রণয়ন |
স্বচ্ছ নিয়োগনীতি প্রতিপালিত |
মধ্যমেয়াদে |
এনজিও ব্যুরো |
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ |
|
৬. |
এনজিও ও সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের দ্বৈততা পরিহার |
সরকার ও এনজিওর উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পূরক কার্যক্রম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত |
দীর্ঘমেয়াদে |
এনজিওসমূহ; এনজিও বিষয়ক ব্যুরো |
তত্ত্বাবধানে: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় |
৩.৪ পরিবার
৩.৪.১ প্রেক্ষাপট
মানুষের নৈতিক জীবন ও নৈতিকতার মূল ভিত্তি হল পরিবার থেকে গড়ে-ওঠা মূল্যবোধ। জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ যে নৈতিক মূল্যবোধ লালন ও অনুসরণ করে তার উৎস হচ্ছে পরিবার। সহস্র বছরের ঐতিহ্যবাহী সভ্যতা ও সংস্কৃতির পাদপীঠ বাংলাদেশ। এ সমাজে পারিবারিক ঐতিহ্য আবহমান কাল ধরে টিকে আছে এবং তা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের নগরায়ন, বিশ্বায়ন, অর্থনৈতিক জীবনের দ্রুত প্রসার ও উন্নয়ন, প্রযুক্তি, বিশেষত তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, গণমাধ্যমের প্রসার, টেলিভিশন ও প্রমোদ-বাণিজ্যের বিস্ফোরণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশ্বায়ন ও দ্রুত প্রসার, বৈশ্বিক ও দেশীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি এবং শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ পরিবারের সংস্কৃতিকে প্রভূতভাবে প্রভাবিত করছে এবং ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধকে দ্রুত পরিবর্তিত করছে। ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলনকেও তা প্রভূতভাবে প্রভাবিত করছে।
৩.৪.২ চ্যালেঞ্জ
এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:
- পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ়করণ;
- পরিবারে নৈতিক শিক্ষাদানকে প্রসারিত ও জোরদারকরণ;
- ‘রোল মডেলদের’ কার্যক্রম উৎসাহিতকরণ।
৩.৪.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ
লক্ষ্য
পরিবারকে নৈতিক মূল্যবোধের উৎস হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।
দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ:
- শিশুদের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব প্রদান করার ক্ষেত্রে পিতামাতাদের উৎসাহ জোগানো;
- নাগরিকদের স্বেচ্ছা-উদ্যোগে উৎসাহ প্রদান;
- ‘রোল মডেলদের’ কর্ম ও কীর্তির প্রচার ও প্রসার ঘটানো;
- শিশুকিশোর, পিতামাতা এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান তথা বিদ্যালয়, ধর্ম ও ন্যায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মধ্যকার অধিকতর যোগাযোগ উৎসাহিতকরণ।
৩.৪.৪ কর্মপরিকল্পনা
|
ক্রমিক |
কার্যক্রম |
কর্মসম্পাদন সূচক |
সময় |
দায়িত্ব |
সহায়তাকারী |
|
১. |
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মাতাপিতাদের (parents) মত বিনিময়ের আয়োজন করা |
সভা অনুষ্ঠিত ও কার্যক্রম পরিচালিত |
চলমান |
স্থানীয় সরকার বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় |
পিতামাতা, বিদ্যালয় ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ |
|
২. |
শিশু-কিশোর ও তরণ-তরুণীদের স্বেচ্ছাসেবা, দেশপ্রেম ও জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান |
উল্লিখিত কর্মকাণ্ডে শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণীদের অধিক হারে অংশগ্রহণ |
চলমান |
স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিদ্যালয়সমূহ |
পিতামাতা, সুশীল সমাজ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ |
|
৩. |
‘রোল মডেলদের’ কর্ম ও কীর্তির প্রচার প্রসার ঘটানো |
কার্যক্রমের প্রচার ও প্রসার সম্পর্কিত প্রতিবেদন |
দীর্ঘমেয়াদে |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান; শিক্ষা মন্ত্রণালয়; সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
মিডিয়া, সুশীল সমাজ |
|
৪. |
শিক্ষাগত ও পেশাগত উন্নয়ন বিষয়ে কমিউনিটিভিত্তিক শিশু ও যুব কল্যাণ কেন্দ্রসমূহকে সহায়তা দান |
কার্যক্রমে পিতামাতার উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ |
চলমান |
স্থানীয় সরকার বিভাগ |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ |
৩.৫ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান
৩.৫.১ প্রেক্ষাপট
পরিবারের পর যে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মানুষের নৈতিক জীবনে সবচেয়ে বেশি ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে, তা হল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানে শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণীরা যেমন বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য, সেবা ও দক্ষতা লাভ করে তেমনই নৈতিক ধারণা ও প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপদ্ধতির কয়েকটি ধারা রয়েছে যেগুলির মধ্যে বাংলা ভাষাভিত্তিক মূলধারার শিক্ষা-ব্যবস্থা, ইংরেজি ভাষাভিত্তিক শিক্ষা-ব্যবস্থা, ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রিক ও আরবি ভাষাভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্যে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষাধারা উল্লেখযোগ্য। সকল শিক্ষাধারায়ই নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে এ বিষয়ে সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানের অভাব, এবং বিভিন্ন ধারায় গুরুত্ব প্রদানের তারতম্যের কারণে এগুলির কার্যকারিতায় তারতম্য ঘটছে।
৩.৫.২ চ্যালেঞ্জ
এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:
- শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর সামাজিক তত্ত্বাবধান;
- নৈতিকভাবে শুদ্ধ জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষা ও ধর্মবিশ্বাসভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বতঃতৎপর ভূমিকা পালন;
- সহায়ক শিক্ষণ পদ্ধতিসহ পর্যাপ্ত সামগ্রী ও সম্পদ প্রদান।
৩.৫.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ
লক্ষ্য
নৈতিকতা শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকর প্রভাব-বিস্তারকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে শিক্ষা ও ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিষ্ঠালাভ।
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ
- নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণ ও ধর্মভিত্তিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর সক্ষম করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়তা দান;
- সাধারণ শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো;
- উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থানীয় প্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের তদারকি বৃদ্ধি ও তাদের সুপারিশ বাস্তবায়ন;
- মেয়েদের উপবৃত্তির পরিসর বৃদ্ধি।
৩.৫.৪ কর্মপরিকল্পনা
|
ক্রমিক |
কার্যক্রম |
কর্মসম্পাদন সূচক |
সময় |
দায়িত্ব |
সহায়তাকারী |
|
১. |
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম জোরদারকরণ |
জাতীয় সঙ্গীতের পর নৈতিকতা শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালনা; সকল বিদ্যালয়ে বয়স্কাউট ও গার্লসগাইড কার্যক্রম বাস্তবায়ন |
মধ্যমেয়াদে |
শিক্ষা মন্ত্রণালয়; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় |
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
|
২. |
সাধারণ শিক্ষায় নৈতিক শিক্ষার পাঠক্রম ও উপযুক্ত শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তন |
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাসূচিতে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ |
মধ্যমেয়াদে |
শিক্ষা মন্ত্রণালয়; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় |
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
|
৩. |
বিদ্যালয় ও ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তদারকিতে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সম্পৃক্তকরণ |
স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিগণ তদারকি কার্যে অন্তর্ভুক্ত; নিরপেক্ষ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে ম্যানেজিং কমিটি গঠিত |
মধ্যমেয়াদে |
শিক্ষা মন্ত্রণালয়; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় |
স্থানীয় সরকার বিভাগ |
|
৪. |
মেয়ে-শিশুদের উপবৃত্তির পরিসর বৃদ্ধি |
অধিকসংখ্যক মেয়েশিশুর উপবৃত্তি লাভ |
মধ্যমেয়াদে |
শিক্ষা মন্ত্রণালয়; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় |
স্থানীয় সরকার বিভাগ |
৩.৬ গণমাধ্যম
৩.৬.১ প্রেক্ষাপট
(ক) মুদ্রণ এবং ইলেকট্রনিক প্রচার-মাধ্যম সহযোগে গঠিত বাংলাদেশের গণমাধ্যমে সাম্প্রতিককালে একটি বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪৭১টি দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক. ত্রৈমাসিক ও ষাণ্মাসিক পত্রিকা মিডিয়া-লিস্টভুক্ত (এর মধ্যে ৩২০টি সংবাদপত্র দৈনিক)। ১১টি বেসরকারি এফ.এম বেতারকেন্দ্র, ১৪টি কমিউনিটি রেডিও, বেশ কয়েকটি কেন্দ্রের মাধ্যমে সরকারি রেডিও – ‘বাংলাদেশ বেতার’ এবং ৩টি সরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এবং ২৭টি বেসরকারি চ্যানেল নিয়মিতভাবে তথ্য সংগ্রহ, প্রচার ও সম্প্রচারের কাজ করে চলেছে। রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, ভিত্তিহীন ও বিকৃত সংবাদ প্রচার রোধ এবং এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
(খ) বাংলাদেশে গণমাধ্যম বিপুল পরিসরে স্বাধীনতা ভোগ করে – সংবাদ সংগ্রহ, নির্বাচন এবং প্রচার ও সম্প্রচারের ক্ষেত্রে তাদের ওপর কোনও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা হয় না। তবে, সরকার পরিচালিত গণমাধ্যম, রেডিও ও টেলিভিশন সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি ও উন্নয়ন উদ্যোগের ওপর গুরুত্ব দিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাশ হওয়ার ফলে সাংবাদিকগণ সহজে বিভিন্ন সংবিধিবদ্ধ ও অন্য প্রকার সংস্থা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হচ্ছেন।
(গ) সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে পূর্ণ নিরাপদ অবস্থা নিশ্চিত করা সময়সাপেক্ষ। কখনও কখনও তাদেরকে ভীতিপূর্ণ ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়; তারা মাঝেমধ্যে সহিংসতারও শিকার হচ্ছে। এ ধরনের সমস্যার নিরসন করা প্রয়োজন। পাশাপাশি গণমাধ্যমের অধিকতর দায়বদ্ধতা ও পেশাগত নৈতিকতা বজায় রাখা আবশ্যক। খবর পরিবেশনের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতা অত্যন্ত জরুরি; দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার অভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্রান্তিপূর্ণ ও পক্ষপাতমূলক খবর পরিবেশিত হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং ব্যবসায়িক স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিতকরণে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, তা-ই প্রত্যাশিত।
৩.৬.২ চ্যালেঞ্জ
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আওতায় গণমাধ্যম কর্তৃক যাচিত তথ্য লাভ;
- গণমাধ্যমের বিচ্যুতি সম্পর্কে প্রেস কাউন্সিলের স্বতঃপ্রবৃত্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ব্যবসায়িক ও দলগত স্বার্থমুক্ত নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ গণমাধ্যমের প্রতিষ্ঠা;
- সাংবাদিকদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন এবং এর অনুসরণ;
- সাংবাদিকদেরকে সার্বিক নিরাপত্তা বিধান।
৩.৬.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ
লক্ষ্য
নাগরিকদের কণ্ঠস্বর হিসাবে স্বাধীন, পক্ষপাতহীন ও দায়বদ্ধ গণমাধ্যমের প্রতিষ্ঠা।
স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ
- সংবাদকর্মীদের সংবাদ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পরিবেশনার ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন;
- গণমাধ্যমের সহায়তায় নিবিড় পরামর্শক্রমে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন;
- সরকারি বিজ্ঞাপন নীতি পর্যালোচনা এবং এতে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ
- সাংবাদিকদের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন;
- গণমাধ্যম-প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রমিত সম্পাদকীয় নীতি এবং এ পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য আচরণবিধি প্রবর্তন;
- জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে যথাযথ পারিতোষিক ও সুবিধাদি প্রদান;
- গণমাধ্যমের সম্পাদনা ও ব্যবস্থাপনার পৃথকীকরণের মাধ্যমে সম্পাদকীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ।
৩.৬.৪ কর্মপরিকল্পনা
|
ক্রমিক |
কার্যক্রম |
কর্মসম্পাদন সূচক |
সময় |
দায়িত্ব |
সহায়তাকারী |
|
১. |
তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ |
বিধি ও পদ্ধতি অনুসারে সরকারি দপ্তর থেকে নাগরিক ও গণমাধ্যমের তথ্য লাভ |
চলমান |
তথ্য কমিশন |
তথ্য ও অন্যান্য মন্ত্রণালয় |
|
২ |
পক্ষপাতহীন ও স্বচ্ছ সরকারি বিজ্ঞাপন নীতি অনুসরণ |
উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সরকারি বিজ্ঞাপন প্রচারিত |
স্বল্পমেয়াদে |
তথ্য মন্ত্রণালয় |
গণমাধ্যম সংস্থাসমূহ; সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ |
|
৩. |
গণমাধ্যমে শুদ্ধাচার নিশ্চিতকরণ |
গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন, প্রতিপালন ও বাস্তবায়ন |
স্বল্পমেয়াদে |
গণমাধ্যমের সংস্থাসমূহ |
তথ্য মন্ত্রণালয়; প্রেস কাউন্সিল |
|
৪. |
সাংবাদিকদের জন্য ‘ওয়েজ বোর্ডের’ সুপারিশ বাস্তবায়ন |
গণমাধ্যম কর্মীদের ওয়েজ বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি লাভ |
মধ্যমেয়াদে |
গণমাধ্যমের সংস্থাসমূহ |
তথ্য মন্ত্রণালয় |
|
৫. |
সংবাদকর্মীদের সংবাদ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজতকরণ ও পরিবেশনার ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন |
বহুমুখী প্রশিক্ষণ কোর্সে কর্মী ও সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ লাভ। ভ্রান্তিপূর্ণ ও পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ প্রচার নিরসন। |
চলমান ও দীর্ঘমেয়াদে অধিকতর কার্যক্রম গ্রহণ |
গণমাধ্যমের সংস্থাসমূহ |
তথ্য মন্ত্রণালয় |
|
৬. |
গণমাধ্যমের ‘ওয়াচডগ’ হিসাবে প্রেস কাউন্সিলের জোরদারকরণ |
গণমাধ্যমের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রেস কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন |
স্বল্পমেয়াদে এবং অব্যাহতভাবে |
প্রেস কাউন্সিল |
গণমাধ্যম সংস্থাসমূহ |
|
৭. |
সাংবাদিকদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি |
গণমাধ্যম কর্মীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ঘটনার নিরসন |
স্বল্পমেয়াদে এবং অব্যাহতভাবে |
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় |
গণমাধ্যম সংস্থাসমূহ |
|
৮. |
তথ্য কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি |
তথ্য কমিশনের জন্য পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ ও উপকরণ সরবরাহ |
মধ্যমেয়াদে ও অব্যাহতভাবে |
তথ্য মন্ত্রণালয় |
অর্থ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় |
অধ্যায় ৪: বাস্তবায়ন ও উপসংহার
৪.১ বাস্তবায়ন ব্যবস্থা
(ক) রাষ্ট্রে ও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা সরকারের সাংবিধানিক ও আইনগত স্থায়ী দায়িত্ব; সুতরাং সরকারকে অব্যাহতভাবে এই লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এই দলিলটিতে শুদ্ধাচার অনুসরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনকানুন, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতির একটি বহুধাবিস্তৃত ও সম্মিলিত রূপ সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। এসব ব্যবস্থা ও পদ্ধতির উন্নয়ন ও সংস্কারের প্রস্তাবও করা হয়েছে এতে। মূলত নির্বাহী বিভাগের আওতাধীন জনপ্রশাসনের মাধ্যমেই এই শুদ্ধাচার কৌশলটি বাস্তবায়ন করা হবে। কৌশলটিতে রাষ্ট্রের অন্য দুটি অঙ্গ – বিচার বিভাগ এবং আইনসভা এবং সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের জন্যও কর্মসূচি প্রস্তাব করা হয়েছে। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার উচ্চ গুরুত্ব বিবেচনা করে এসব প্রতিষ্ঠান স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে চিহ্নিত পথরেখা অনুসরণে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন এসব প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি সহায়তা দেবে এবং সম্পদ সরবরাহ করবে। সুশীল সমাজ ও শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও জনপ্রশাসন সহযোগিতা প্রদান করবে এবং কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবে। কৌশলটিতে চিহ্নিত কার্যক্রম সময়নির্ধারিত, কিন্তু শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি কোন সময়ের পরিসরে সীমিত নয়; সুতরাং এই কৌশলও অব্যাহতভাবে উন্নত ও পরিশীলিত করতে হবে; এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নেও পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধন করতে হবে।
(খ) এই ‘শুদ্ধাচার কৌশল’টি বাস্তবায়নের জন্য একটি ‘জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ’ গঠন করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদের কয়েকজন সদস্য, কয়েকজন আইনপ্রণেতা, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সচিব, এনজিও ও সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম এবং ব্যক্তিখাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক-প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে এই উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হবে। সুশীল সমাজ, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমের সদস্যগণ পরিষদে সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। এই উপদেষ্টা পরিষদ বছরে অন্ততপক্ষে দু’বার সভায় মিলিত হবে এবং শুদ্ধাচার অনুশীলন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ করবে এবং এ সম্পর্কিত দিক্-নির্দেশনা প্রদান করবে। কাজের সুবিধার্থে এ পরিষদের নির্বাহী কমিটি গঠন করা যাবে।
(গ) মন্ত্রিপরিষদ সচিবের তত্ত্বাবধানে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক সংস্কার ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একটি ইউনিট ‘জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট’ হিসাবে কাজ করবে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও উল্লিখিত সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে ‘নৈতিকতা কমিটি’ গঠন করা হবে। নৈতিকতা কমিটির একজন কর্মকর্তাকে ‘ফোকাল পয়েন্ট’ হিসাবে মনোনীত করে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে ‘শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট’ প্রতিষ্ঠা করা হবে। এনজিও ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের বিষয়াদি তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করবে যথাক্রমে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। বিদ্যমান ‘অভিযোগ ব্যবস্থার ফোকাল পয়েন্ট’-কে শুদ্ধাচার সম্পর্কিত কার্যক্রমের ‘ফোকাল পয়েন্টের’ দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ইউনিট’ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানকে নৈতিকতা ফোকাল পয়েন্ট-এর মাধ্যমে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে বিধৃত কর্মপরিকল্পনা অনুসরণে বিস্তারিত কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করবে।
(ঘ) ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ সময়ে সময়ে সংশোধনের প্রয়োজন হবে। ‘জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ’-এর সুপারিশ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে এ কৌশলপত্র সংশোধন করা যাবে।
৪.২ পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা
(ক) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন ‘জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের’ নির্দেশনা অনুযায়ী ‘জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট’ মন্ত্রিপরিষদ সচিবের তত্ত্বাবধানে শুদ্ধাচার সম্পর্কিত সকল নীতি-নির্ধারণ, কার্যক্রম-বাস্তবায়ন ও তাদের সমন্বয়, অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং নতুন নীতি ও কৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ‘ফোকাল পয়েন্ট’ হিসাবে কাজ করবে। মন্ত্রণালয় ও প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে গঠিত ইউনিটসমূহ তাদের কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি জাতীয় বাস্তবায়ন ইউনিটে রিপোর্ট করবে এবং জাতীয় বাস্তবায়ন ইউনিট তা সমন্বয় করবে। সুশীল সমাজ ও এনজিওসমূহের শুদ্ধাচার কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ করবে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, এবং বেসরকারি শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতের শুদ্ধাচার কার্যক্রম বিভিন্ন বণিক ও শিল্পসমিতির মাধ্যমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত ও পরিবীক্ষিত হবে। এই লক্ষ্যে এনজিওসমূহে ও শিল্প ও বণিক সমিতিসমূহে শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট গঠনের জন্য যথাক্রমে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গাইডলাইন প্রণয়ন করবে এবং তা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ‘শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ইউনিট’ সাংবিধানিক সংস্থাসমূহকে শুদ্ধাচার কৌশল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ‘নৈতিকতা কমিটি’ ও ‘ফোকাল পয়েন্ট’ গঠনে উৎসাহ প্রদান করবে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে।
(খ) ‘জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট’ শুদ্ধাচার সম্পর্কিত সকল প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও সমন্বয় করে তা জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবে। বাস্তবায়ন ইউনিট জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের সকল নির্দেশনা ও পরামর্শ মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য ইউনিটকে অবগত করবে এবং তাদের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করবে। পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য বাস্তবায়ন ইউনিট প্রয়োজনবোধে কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকেও নিয়োগ করতে পারবে। এক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনা, বিশেষ প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহ, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতির উন্নয়ন এবং লোকবলের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় ইউনিট যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
(গ) সরকারি, বেসরকারি খাত ও সুশীল সমাজের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ এবং শুদ্ধাচার পালন ও তাতে সহায়তাদানের জন্য পুরস্কৃত করলে সর্বক্ষেত্রে শুদ্ধাচার অধিকতর উৎসাহিত হবে। সেই লক্ষ্যে সরকার নির্বাহী বিভাগ, ব্যবসায় খাত ও সুশীল সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে যারা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবেন, তাদের জন্য বার্ষিক পুরস্কার প্রবর্তন করবে।
৪.৩ উপসংহার
বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত উদ্যোগ হিসাবে এই কৌশলপত্রটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে রাষ্ট্র, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাতের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। বিদ্যমান আইনকানুন, নিয়মনীতির সংস্কার সাধন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন আইন ও পদ্ধতি প্রণয়ন করে মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার নতুন প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসও প্রস্তাব করা হয়েছে।
এই কৌশলটি একটি বিকাশমান দলিল। শুদ্ধাচারের ওপর গুরুত্ব দিয়ে ‘প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১’-এ দুর্নীতি দমনকে একটি আন্দোলন হিসাবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। সেই অঙ্গীকারকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই সরকার এই ‘শুদ্ধাচার কৌশল’ প্রণয়ন করেছে। আশা করা যায় যে, সোনার বাংলা গড়ার পথে এই কৌশল ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে।